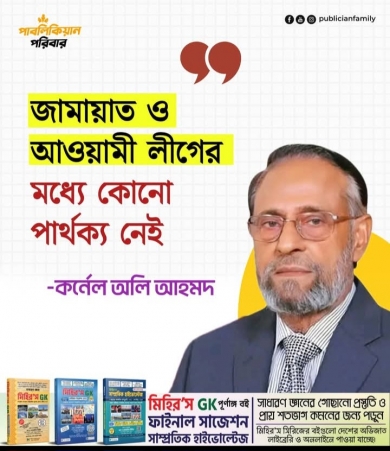আমাদের জানামতে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বে এখন পর্যন্ত আলোর বেগই হচ্ছে সর্বোচ্চ বেগ। আলো কি এবং আলোর বেগ কত, তা জানার জন্য আলোর ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের প্রথমে একটু আলোকপাত করা উচিত। কারণ, সর্বোচ্চ বেগের অধিকারী এই অপদার্থ (আলো যেহেতু পদার্থের সংজ্ঞা মানেনা, তাই একে অপদার্থ বলাটাই শ্রেয়) আসলে কি, তা আমাদের জানার চেষ্টা করা উচিত।
আলোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
প্রাচীনকাল থেকেই আলো কি, সেটা নিয়ে মানুষের নানারকমের ভাবনা ছিল মাথায়। রহস্যময় এই আলোর কোনও ব্যাখ্যা তারা খুঁজে পেতনা। ইতিহাসের ঘড়ি যতদূর সম্ভব পেছনে ঘুরালে আমরা দেখতে পাই খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস ও প্লেটো সর্বপ্রথম আলো সম্পর্কে একটি ধারণা দেন। তাঁদের ভাষ্যমতে আলো এক ধরণের রশ্মি, যা আমাদের চোখ থেকে নির্গত হয়ে বস্তুর ওপর আপতিত হয়। অতঃপর বস্তু থেকে ওই রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়লে তখন আমরা ওই বস্তুকে দেখতে পাই। ধারণাটা বেশ সহজ হলেও বা তখনকার সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য হলেও আজকের যুগে সেটা যে অচল বা হাস্যকর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে কারও মাথায়ই এ প্রশ্নটি সহজেই খেলে যাবে যে, তাহলে রাতের অন্ধকারে আমরা দেখতে পাইনা কেন? রাতের বেলায় আমাদের চোখে কি সমস্যা দেখা দেয়? দিন আর রাত মূলত সূর্যের উঠানামার সাথে সম্পর্কিত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে তখন, আলো কি আমাদের চোখের সাথে সম্পর্কিত, নাকি সূর্যের সাথে? আলো নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানা ধারণা, চিন্তা বা সন্দেহ পোষণ করে আসছিল।
বিশ্ববরেণ্য ইংরেজ বিজ্ঞানী, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবর্তক যাকে বলা হয়, সেই আইজ্যাক নিউটন অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে আলোর কণিকা তত্ত্ব প্রদান করেন। স্যার আইজ্যাক নিউটনের এই তত্ত্বানুসারে আলো হল এক ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার ঝাঁক। কোনও দীপ্ত বস্তু হতে (যেমন-সূর্য, আগুন) যখন আলোক কণিকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে নির্গত হয়ে কোনও বস্তুর উপর আপতিত হয়, তখন সেগুলো সেখান থেকে প্রতিফলিত হয় এবং এরপর আমাদের চোখে এসে আপতিত হয়। ফলে আমাদের চোখে তখন ওই বস্তু সম্পর্কে দর্শনের অনূভুতি জন্মায়। এই কণাগুলো তাদের উৎস থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এদের পথ সরল রৈখিক এবং এগুলো ওজনহীন। নিউটনের এই কণাতত্ত্ব আলো সম্পর্কিত অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম হয়। যেমন- আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ।
স্বাভাবিকভাবেই ভাবলে দেখা যায় যে, আলো যদি সরল পথে চলে, তাহলে এটির কোনও বস্তুর উপর আপতন ও সেখান থেকে প্রতিফলন হওয়ার ঘটনাটা বেশ সহজে বুঝতে পারা যায়। প্রতিসরণের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় আলোর আরও কিছু ঘটনাবলী নিয়ে, যেগুলোকে আলোর কণাতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়না। যেমন- আলোর ব্যাতিচার, অপবর্তন, বিচ্ছুরণ ইত্যাদি। কোনও অন্ধকার রুমে একটি উৎস হতে একরঙা আলো নির্গত হয়ে যদি সামনে রাখা কোনও প্রতিবন্ধকের দুটি চিড় বা ফাটলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে কোনও পর্দায় এসে আপতিত হয়, তাহলে দেখা যায় যে সেখানে পরপর অনেকগুলো সাদা ও কালো ডোরার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাকে বলা হয় আলোর ব্যাতিচার।
এই ব্যাতিচারকে কণা তত্ত্ব দিয়ে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা দেবেন? আলো যদি কণার ঝাঁক হয় এবং সরলপথে চলে, তাহলে এই কণাগুলো ফাটল দুটোর মুখ দিয়ে বেরিয়ে তো আবারও সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়ে পর্দায় উজ্জ্বল আভার সৃষ্টি করার কথা। কিন্তু তার বদলে আপনি পাচ্ছেন সাদা ও কালো ডোরার আলোকীয় নকশা। কেন? আবার কোনও প্রিজমের উপর সূর্যের আলো এসে আপতিত হয়ে সাতটি আলাদা রঙে বিশ্লিষ্ট বা বিচ্ছুরিত হয়ে অনেকটা রংধনুর মত আভা সৃষ্টি করে। এই ঘটনাকে বলা হয় আলোর বিচ্ছুরণ। এই বিচ্ছুরণের ব্যাখ্যাই বা কি? আলো যদি কণাই হয়ে থাকে, তাহলে প্রিজমে এসে আলাদাই বা হবে কেন, আর আলাদা হলেও আলাদা আলাদা রঙ তৈরি করবে কেন? এইসব ঘটনার কারণে স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীরা কণা তত্ত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন।
আলোর এই ব্যাতিচার, বিচ্ছুরণ, অপবর্তন বা সমবর্তন এ ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় যদি আলোকে কণা না ধরে তরঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিজ্ঞানী হাইগেনস ১৬৭৮ সালে, মানে নিউটনের সমসাময়িক সময়েই আলোর তরঙ্গতত্ত্ব উথাপন করেন। তাঁর মতে আলো হচ্ছে নিজ উৎস থেকে ছড়িয়ে পড়া একধরণের তরঙ্গ। কোনও পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন উৎস থেকে পানির তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আলোও অনেকটা সেরকম উৎস হতে উৎপন্ন হয়ে চতুর্দিকে তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে। যদি আলোকে তরঙ্গ ধরা হয় তাহলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে উপরোল্লেখিত ঘটনায় (ব্যাতিচার ও বিচ্ছুরণ) আলো কেন পর্দার মধ্যে সাদাকালো ডোরার সৃষ্টি করে ও প্রিজমে এসে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। প্রথম ঘটনার ক্ষেত্রে, আলো একটি উৎস হতে উৎপন্ন হয়ে দুটি ফাটলের মধ্যে তরঙ্গাকারে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর এই তরঙ্গদ্বয় পর্দায় এসে যেখানে যেখানে সমদশায় মিলিত হয়, সেখানে উজ্জ্বল বা সাদা ডোরার সৃষ্টি করে এবং যেখানে যেখানে বিপরীত দশায় মিলিত হয়, সেখানে অন্ধকার, কালো ডোরার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে মানে বিচ্ছুরণের ব্যাখ্যায় বলা যায়, সূর্যের আলো তরঙ্গাকারে কোনও প্রিজমে এসে আপতিত হয়ে মৌলিক রঙের তরঙ্গে আলাদাভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়।
সূর্যের সাদা আলো আসলে সাতটি রঙ মিলে তৈরি। কেউ সেটা পরীক্ষা করতে চাইলে সাদা গোলাকার শক্ত কোনও কাগজের চাকতি নিয়ে তার মধ্যে সাতটি সমান মাপের ছেদাংশ অঙ্কন করুন। সেই সাত অংশে সাতটি বেগুনী, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল- এই সাত রঙে ভরাট করুন। এবার সেই সাত রঙা চাকতির কেন্দ্রে কোনও সরু ও লম্বা কাঠি ঢুকিয়ে দুই হাত দিয়ে ঘষে প্রবল বেগে ঘুরাতে থাকুন। দেখবেন, ঘূর্ণনরত অবস্থায় চাকতির মধ্যে স্রেফ সাদা রঙ দেখা যাচ্ছে, সাত রঙের অন্য কোনও রঙই দেখা যাচ্ছেনা। এই ঘটনাটি স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, সাদা রঙ আসলে মৌলিক কোনও রঙ নয়, বরং সাতটি আলাদা আলাদা রঙের সমষ্টি। সূর্যের আলো আসলে তাই। এর আলোর রঙ মৌলিক কোনও রঙ নয়। সাতটি আলাদা রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য মিলেই সূর্যের সাদা যৌগিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সৃষ্টি করে। সূর্যের এই সাদা আলো যখন প্রিজমে, মানে বিশেষভাবে তৈরি ত্রিভুজাকার কাঁচ মাধ্যমে এসে আপতিত হয়, তখনই আলাদা আলাদা রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলো বাধা পেয়ে আলাদা হয়ে যায়। ফলে আমরা তখন এদের আলাদা সাতটি রঙে দেখতে পাই। এই ঘটনাকেই আলোর বিচ্ছুরণ বলে, যা স্রেফ আলোর তরঙ্গতত্ত্বই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। পরবর্তিতে বিজ্ঞানী টমাস ইয়ং ও ফ্রেনেল এ তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।
অপরদিকে বিজ্ঞানী আলমন্ড ফিজো ভূতাত্ত্বিক একটি পরীক্ষার মাধ্যমে আলোর গতিবেগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন ১৮৪৯ সালে। তিনি এই পরীক্ষায় একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র, একটি আলোক উৎস, তিনটি লেন্স, একটি অবতল দর্পন ও একটি দাঁতওয়ালা চাকা ব্যবহার করেন। তাঁর পরীক্ষা পদ্ধতিতে কিছুটা ত্রুটি থাকায় আলোর বেগের একেবারে নিখুঁত মান তিনি বের করতে পারেননি। তবে প্রায় কাছাকাছি মান বের করে ফেলেছিলেন। তাঁর প্রাপ্ত মান ছিল ৩.১৩×〖১০〗^(৮ ) মিটার/সেকেন্ড। পরে ১৮৬২ সালে ফুঁকো একে সংশোধন করে পরীক্ষা করে আলোর নিখুঁত মান নির্ণয় করেন প্রায় ২.৯৯×〖১০〗^(৮ ) মিটার/সেকেন্ড। অর্থাৎ আলো প্রতি সেকেন্ডে ২.৯৯×〖১০〗^(৮ ) মিটার বা ১,৮৬০০০ মাইল অতিক্রম করে! অকল্পনীয় বেগ! কোনও মানুষ তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত আমাদের জানা মতে এমন কোনও পদার্থ বা কোনও কণা নেই এই মহাবিশ্বে, যা এই বেগকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।
১৮৪৫ সালে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কার করেছিলেন যে, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক শক্তির মধ্যে কোনও একটা সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু বিদ্যুৎ আলো উৎপন্ন করে, সুতরাং চৌম্বক শক্তির সাথেও বিদ্যুতের সম্পর্ক রয়েছে। ১৮৬৪ সালে এসে বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল তাঁর বিখ্যাত সমীকরণের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করা যায়। যেমন- কোনও লোহাকে প্রবাহী তার দিয়ে পেঁচিয়ে সেই কুন্ডুলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করলে তারের কুন্ডুলীর ভেতরে থাকা লোহাটা কিন্তু তখন সাময়িকভাবে চুম্বকের মত আচরন করবে। ম্যাক্সওয়েল দেখান যে, তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্র মিলে শূন্যস্থানে এক প্রকার আলোড়ন বা তরঙ্গের সৃষ্টি করে। একে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বলে। যেমন- বেতার তরঙ্গ, অবলোহিত তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি।
ম্যাক্সওয়েল তখন ওই তরঙ্গের গতিবেগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এবং হিসেব কষে তিনি যে গতিবেগ নির্ণয় করেন, বিস্ময়ের সাথে তিনি দেখেন যে, সেটা আলোরই বেগ! অর্থাৎ আলো এক প্রকার তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। তবে স্রেফ আলো নয়, আরও অনেক প্রকার তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ রয়েছে, যেগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পাইনা। আমরা যাকে আলো বলি, বা দেখি, সেটা হচ্ছে এক প্রকার দৃশ্যমান তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। আর বাকিগুলোকে আমরা দেখতে পাইনা। রোদের আলোর সাথে আসা অতিবেগুনী রশ্মি, এক্স রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ, বেতার তরঙ্গ, অবলোহিত তরঙ্গ- এ সবই হচ্ছে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। এদের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে স্রেফ এদের আলাদা আলাদা তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ তরঙ্গে তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্র পরস্পর সমকোণে থেকে ছন্দিত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।
হাইগেনসের প্রবর্তিত তত্ত্ব থেকে আমরা পেয়েছিলাম যে, আলো হচ্ছে এক প্রকার তরঙ্গ। কিন্তু বিজ্ঞানী হাইগেনস একটা সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভেবে দেখলেন সব তরঙ্গই কোনও না কোনও মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়। যেমন, পানিতে ঢিল ছুঁড়লে উৎপন্ন তরঙ্গ পানির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এক্ষেত্রে মাধ্যম হল পানি। একইভাবে শব্দ তরঙ্গও বাতাসের মধ্যে আলোড়ন তৈরি করে স্থানান্তরিত হয়ে আমাদের কানের পর্দায় এসে ধাক্কা দেয়। এক্ষেত্রে মাধ্যম হল বাতাস। কিন্তু এবার প্রশ্ন হল- তাহলে আলোক তরঙ্গ কোন মাধ্যম দিয়ে প্রবাহিত হয়? সূর্য থেকে কোটি কোটি মাইল দূরত্ব পেরিয়ে মহাশূন্যের শূন্যতার ভেতর দিয়ে আলো কিভাবে এসে আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছায়?
এই সমস্যার সমাধানের জন্য হাইগেনস মত পোষণ করেন যে, মহাবিশ্বের সর্বত্র ইথার নামে এক ধরণের কাল্পনিক মাধ্যম বিরাজ করছে। এই ইথারের মধ্য দিয়ে আলোক তরঙ্গ সঞ্চালিত হয়। এবার সমস্যা দেখা দিল ইথারের অস্তিত্ব নিয়ে। ইথারের অস্তিত্ব নির্ণয়ের জন্য এবার বিজ্ঞানীদের মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সমস্যা হল, যা নেই তা আপনি প্রমাণ করবেন কিভাবে? ইথার বলে যদি কিছু থেকেই থাকে, তাহলে এর অস্তিত্ব আমরা টের পাই না কেন? তাছাড়া ইথার বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে কিছুটা গতিশীল হবে বা সময়ের ব্যবধানে বিচ্যুত হবে।
আমরা ইথারকে আমাদের কোনও ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারিনা। এক্ষেত্রে যেকেউ দাবি করতে পারেন যে, সবকিছু ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পাওয়া যায়না। যেমন- কোনও জীবাণুকে আপনি হাতে নিয়ে চোখ দিয়ে দেখতে পারবেন না। কারণ, এটা এতই ক্ষুদ্র যে তা আপনি হাতে নিলে এর অস্তিত্বও টের পাবেন না, খালি চোখে দেখা তো অনেক দূরের ব্যাপার। এক্ষেত্রে আপনি আণুবীক্ষণিক যন্ত্রের সাহায্য একে দেখতে পারবেন কিংবা জীবাণুর কার্যকলাপ জানা থাকলে আপনি এর অস্তিত্ব আপনার শরীরে দেখা দেওয়া রোগের মাধ্যমে অনুভব করতে পারবেন। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আপনি জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন। তাই আমাদের উচিত ইথারের অস্তিত্ব নির্নয়ের জন্য কোনও ধরণের একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালানো।
১৮৮৭ সালে অ্যালবার্ট মাইকেলসন ও এডওয়ার্ড মর্লি নামক দুজন পদার্থবিদ ইথারের অস্তিত্ব নির্ণয়ের জন্য একটি পরীক্ষা চালান। তাঁদের ধারণা অনুসারে যদি ইথার নামক কোনও ধরণের মাধ্যম থেকেই থাকে তাহলে সেটা পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে সে নিজেও কিছুটা হলে ঘুরবে। ঠিক যেমন পৃথিবীর বাতাস কিংবা বায়ুমন্ডল পৃথিবীর সাথে সাথে গতিশীল থাকে, অনেকটা সেরকম। ইথার মহাশূন্যে স্থির থাকলেও পৃথিবীতে তার গতিশীল থাকা উচিত। আর যদি ইথার গতিশীল থাকে, তাহলে পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিক বরাবর আলো বেশি বেগে ভ্রমণ করবে। কারণ, তখন আলোর বেগের সাথে পৃথিবীর বেগ যোগ হবে। আবার পৃথিবীর ঘূর্ণনের বিপরীত দিকে আলো নির্গত করলে তখন আলোর বেগ কিছুটা শ্লথ হয়ে যাবার কথা। কারণ, তখন আলোর বেগের থেকে পৃথিবীর বেগ বিয়োগ হবে।
অনেকটা নদীর স্রোতের উপর দিয়ে চলমান নৌকার মত। নৌকা যদি আপনি নদীর স্রোতের দিক বরাবর চালান, তাহলে আপনি বেশি বেগে এগিয়ে যাবেন। কারণ তখন আপনার নৌকার বেগের সাথে স্রোতের বেগও এসে যুক্ত হয়েছে। আবার স্রোতের বিপরীত দিকে নৌকা চালালে আপনার নৌকার বেগ ধীর হয়ে যাবে। কারণ তখন নৌকার বেগের থেকে স্রোতের বেগ বিয়োগ দিতে হচ্ছে।
মাইকেলসন ও মর্লি পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকে, কিংবা ঘূর্ণনের বিপরীত দিকে আলোর বেগ একই থাকে। এমনকি নানা ঋতুতে, নানা অঞ্চল থেকে তাঁরা একই পরীক্ষা বারবার করলেন। এবং প্রতিবারই দেখা গেল- আলোর গতি সর্বদা অভিন্ন। এই ঘটনা থেকে আপনি দুটো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। হয় ইথার স্থির, নয়তো বা পৃথিবী স্থির।
পৃথিবী যে স্থির নয়, এ ব্যাপারে অন্তত আজকের যুগের মানুষের কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, পৃথিবী স্থির হলে দিন-রাত্রির সংঘটন হতনা। সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত কোনোটাই ঘটত না। ফলে, পৃথিবীর একদিকে সর্বদা দিন থাকত এবং অপরদিকে সর্বদা রাত থাকত। তাতে একদিকের সকল প্রাণী দিনের আলোয় থাকতে থাকতে রাত্রের যত কার্যকলাপ সব বন্ধ হয়ে যেত। উদ্ভিদ রাতের বেলায় প্রস্বেদন ঘটায়। প্রস্বেদন না ঘটলে উদ্ভিদ মারা পড়বে। আর উদ্ভিদ মারা পড়লে আমরাও অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়তাম। অপরদিকে, পৃথিবীর অন্যপৃষ্ঠে রাত স্থির হয়ে থাকার জন্য দিনের আলোর অভাবে সকল উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার কারণে না খেয়ে মরত এবং সাথে করে আমরাও অক্সিজেনের অভাবে, আলোক শক্তির অভাবে রাতের অন্ধকারেই মরে যেতাম। ফলে, পৃথিবী ঘুরছে কি ঘুরছে না, সেটা প্রশ্ন করার জন্য কোনও মানুষই বেঁচে থাকত না বা পৃথিবীতে মানুষের কোনোকালে জন্মই হত না। তারমানে আপনার হাতে আর একটা অপশন বাকি। আপনাকে ধরে নিতে হবে ইথার স্থির। তারমানে ইথার মহাশূন্যেও স্থির, পৃথিবীতেও স্থির। বলা যায়, মহাবিশ্বের সকল জায়গায় ইথার স্থির। কিন্তু প্রশ্ন হল- যা সবসময়ই স্থির থাকে, যা আলোকে কখনোই প্রভাবিত করতে পারেনা, আলোর গতিকে মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম হেরফের করতে পারেনা, তার অস্তিত্ব থাকা আর না থাকা- দুটোই তো সমান!
অতএব, মাইকেলসন এবং মর্লি তাঁদের পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ইথার মাধ্যম বলে আসলে মহাবিশ্বে কিছুই নেই।
১৯০০ সালে বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্লাংক আলো নিয়ে একটি নতুন তত্ত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, আলো আসলে তার উৎস থেকে নিরবিচ্ছিনভাবে নির্গত হয় না। এটি বিচ্ছিনভাবে গুচ্ছাকারে বের হয়। আলোর গতি খুব বেশি বিধায় একে আমাদের কাছে নিরবিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি আসলে বিচ্ছিন্নভাবে নির্গত হয়। অনেকটা পানির স্রোতের মত। কল থেকে পানি যদি খুব দ্রুত বেগে বের হয়, তখন আপনার মনে হবে যে পানি একটানা একটি নিরবিচ্ছিন্ন রেখার মত বের হচ্ছে। কিন্তু ট্যাপ ঘুরিয়ে পানির গতি একেবারে শ্লথ করে দিলে দেখবেন পানি বিচ্ছিন্নভাবে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে বের হচ্ছে। আলোও আসলে তাই।
অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাপে দেখা যাবে আলো নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নিয়ে গুচ্ছাকারে বা প্যাকেট আকারে বের হচ্ছে। আর এই একেকটি প্যাকেটকে বলা হয় ফোটন। প্রতি ফোটনে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি থাকে। আলো যে নিরবিচ্ছিন, তার একটি সহজ প্রমাণ হচ্ছে দূর থেকে আসা নক্ষত্রের আলো। যেমন- হিসেব করে দেখা গেছে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে প্রায় ৮ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড সময় লাগে। যদি কোনও কারণে হঠাৎ সূর্যের বাত্তি অফ হয়ে যায়, মানে সূর্যের আলো বিকিরণ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবী সাথে সাথে অন্ধকারাচ্ছন্ন হবেনা। বরং সূর্যের আলোর বিকিরণ বন্ধ হওয়ার ৮ মিনিট পর পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যাবে। যদি আলো নিরবচ্ছিন্ন কোনও রেখা হত, তাহলে সূর্যের সাথে সাথে পৃথিবীও প্রায় একই সময়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হত। যেহেতু ৮ মিনিট পরে অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে, এর অর্থ হল- সূর্য আলোর বিকিরণ বন্ধ করার সাথে সাথে শেষবার যে পরিমাণ আলো নির্গত করেছিল, ওই পরিমাণ আলোর ফোটনগুলো পৃথিবীতে ৮ মিনিট পরে এসে পৌছে তারপর সূর্যের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করবে। এই তথ্যটি সূর্যের উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হলেও এমন নয় যে, এরকম বাস্তব কোনও উদাহরণ নেই। বরং এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে আমাদের থেকে লক্ষ কোটি মাইল দূরে থাকা নক্ষত্রের ক্ষেত্রে। আপনি রাতের আকাশে যে সকল জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের জ্বলজ্বলে আলো দেখছেন, আপনার কি ধারণা তা ওই সময়কার আলো? এগুলো আসছে লক্ষ কোটি মাইল পাড়ি দিয়ে, যা মূলত লক্ষ থেকে কোটি বছর আগের পুরনো আলো!
অনেক নক্ষত্র আছে যারা কোটি বছর আগেই ফুয়েল শেষ হয়ে যাবার কারণে মারা পড়েছে। হয়ত কোটি বছর আগে শেষবারের মত নির্গত আলো আজ আপনার চোখে এসে পৌঁছেছে এবং আপনি ভাবছেন যে নক্ষত্রটি বুঝি এখনও, এই মূহুর্তে জীবিত আছে! এই উদাহরণ থেকেই আমরা স্পষ্ট প্রমাণ পাই যে, আলো কোনও নিরবচ্ছিন্ন শক্তির স্রোত নয়। বরং আলো ফোটন আকারে শক্তি বহন করে গুচ্ছাকারে চলাচল করে বেড়ায়।
সুতরাং উপরে এখন পর্যন্ত আলোচিত সমস্ত ঘটনার উপর ভিত্তি করে আমরা আলো সম্পর্কে যা যা জানতে পারলাম, তার সার সংক্ষেপ হলঃ
আলো এক প্রকার তরঙ্গশক্তি, যা ফোটন আকারে নির্গত হয়। আলো কোনও মাধ্যম ছাড়াই চলাচল করতে পারে অর্থাৎ আলো শূন্য মাধ্যমেও সঞ্চালিত হতে পারে। আলোক তরঙ্গ হচ্ছে এক প্রকার তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। আলো এক সেকেন্ডে ১,৮৬০০০ মাইল অতিক্রম করে। এই বেগে আলো সমস্ত পৃথিবীর চারপাশে এক সেকেন্ডে ৮ বার ঘুরে আসতে পারবে! আলো ভরহীন, তাই আলো এই অনতিক্রম্য বেগের অধিকারী। সুতরাং মহাবিশ্বের যেকোনো পদার্থকে আলোর বেগ অর্জন করতে হলে ভরশূন্য হতে হবে। কিন্তু ভরশূন্য হওয়া কারো পক্ষে বা কোনও কিছুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আমাদের জানামতে এখন পর্যন্ত পুরো মহাবিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ বেগের অধিকারী হচ্ছে- আলো।
এখন প্রশ্ন হল- এই গতির প্রতিযোগিতায় আলোকে কি কেউ হারাতে পারবে? নাকি আলোই হচ্ছে সমস্ত গতির শেষ সীমারেখা?
আলোর প্রতিযোগীর সন্ধানে
আলবার্ট আইনস্টাইন যখন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রকাশ করেন ১৯০৫ সালে, তখন সেটা রীতিমত চমকে দেয় গোটা দুনিয়াকে। কারণ, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বানুসারে- আলোর বেগ শূন্য মাধ্যমে সর্বদা একই থাকবে।
যেমন ধরুন, আপনি যদি স্থির দাঁড়িয়ে থেকে একটি বল সামনের দিকে ছুঁড়েন, তাহলে বলটি একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে বাউন্স করবে। কিন্তু যদি আপনি চলন্ত কোনও গাড়ি বা সাইকেল থেকে বল ছুঁড়ে মারেন, তাহলে কিন্তু এবার বলের অতিক্রান্ত দূরত্ব আগের চেয়ে আপনার কাছে কম মনে হবে। কারণ, এখন বলের সাথে সাথে আপনি নিজেও গতিশীল। এক্ষেত্রে, বলের গতি থেকে আপনার সাইকেলের বা চলন্ত যানের গতিকে বিয়োগ দিতে হয়েছে। চলন্ত বাসে কোথাও যাওয়ার পথে আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে আপনার বাসকে ওভারটেক করতে থাকা অপর বাসটিকে কিছুটা স্লো মনে হয়। কারণ, আপনার বাসের সাথে সমান্তরাল পথে চলতে থাকা ওই বাসের গতি থেকে আপনার বাসের গতিকে এখানে বিয়োগ দিতে হচ্ছে। অথচ, বাসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও পথচারী কিন্তু ওই বাসের গতিকে কিন্তু আপনার বাসের থেকে অনেক বেশি গতিশীল হিসেবে পর্যবেক্ষন করছে।
এখন, সমস্যা হল একই পরীক্ষা যদি আপনি আলোর ক্ষেত্রে করতে চান, তাহলেই আপনাকে রীতিমত ভিরমি খেতে হবে। ধরুন, আপনি এখন এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বাললেন। তাহলে আলো ১ মিনিটে কত মাইল যাবে? ১৮৬০০০ মাইলকে ৬০ সেকেন্ড দিয়ে গুণ দিলেই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আপনি যদি ঘন্টায় ১০০ কিমি বেগে চলন্ত একটি গাড়ি থেকে মাটিতে রাখা স্থির টর্চ বা কোনও আলোক উৎস থেকে আসা আলোকে আপনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখেন, তাহলে আলোকে কি সামান্য একটু স্লো দেখার কথা নয়? কিংবা ধরুন আপনি ঘন্টায় হাজার হাজার মাইলবেগে চলন্ত কোনও রকেট থেকে আপনার পাশ দিয়ে যাওয়া আলোকে পর্যবেক্ষন করলেন পুরো ১ মিনিট। তাহলে ওই ১ মিনিট ধরে নিশ্চয়ই আলোকে কিছুটা স্লো মনে হবার কথা আপনার কাছে? কারণ, এক্ষেত্রেও তো আলোর বেগের থেকে রকেটের বেগ বিয়োগ হচ্ছে।
কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হল, ওই ১ মিনিট ধরে আপনি মেপে দেখবেন আলো আগের মতই সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেছে! এবার ধরুন আপনি রেগে গিয়ে এমন কোনও কাল্পনিক যানে চড়ে বসলেন যা আপনাকেও আলোর গতিতে নিয়ে চড়ে বেড়াবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আপনি সেই গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামো বা সিস্টেম থেকে দেখবেন যে, আলোর বেগ সেই একই! সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল!
এখন প্রশ্ন হল- আলোর বেগের এই রহস্যময় আচরণের কারণ কি? কেন আলোর বেগ সর্বদা একই থাকছে?
এর উত্তরে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব কি বলে তা আমাদের জানতে হবে। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বানুসারে, আলো যখন কোনও গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামো নিয়ে চলমান থাকে তখন ওই কাঠামোর ঘড়ি স্লো হয়ে যায় এবং কাঠামোর দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়ে যায়। পৃথিবীতে স্থির দাঁড়িয়ে আপনি আলোর যে গতি মাপছেন, মহাশূন্যে চলন্ত কোনও রকেট থেকে আলোর গতিকে মাপলেও আপনি আলোর একই বেগ পাচ্ছেন। এর কারণ, আলোর গতি কিন্তু আসলে ঠিকই কিছুটা স্লো হয়েছে আপনার রকেটের গতি বিয়োগ দেওয়ার কারণে। কিন্তু আপনার রকেটে থাকা ঘড়িটি কিন্তু স্লো হয়ে গেছে ওই সময়। যার ফলে আপনার ১ মিনিট, আর পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকা কারও ১ মিনিট এখন আর সমান নয়! আপনি যত বেশি আলোর গতির কাছাকাছি গতি অর্জন করবেন, আপনার ঘড়িও তত বেশি স্লো হতে থাকবে। ফলে গতি যত কমবে, সময়ের পরিমাণ ততই বাড়বে। অর্থাৎ একটি কমলে আরেকটি বাড়ে, বা আরেকটি কমলে অপরটি বাড়ে, কিন্তু এদের অনুপাত একই থাকে। এই অপরিবর্তনশীল অনুপাত বা ধ্রুবকই হচ্ছে আলোর বেগ। তাই আপনি সবসময় আলোর গতিকে একই দেখবেন। আর যদি কখনও আপনি একেবারে নিখুঁত আলোর বেগ অর্জন করে ফেলেন তাহলে সত্যি কথা হল আপনার ঘড়ি তখন আর স্লো নয়, একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে! আপনিসহ আপনার রকেটের দৈর্ঘ্য ও আপনার অতিক্রম্য দূরত্ব সংকুচিত হয়ে একটি সুতার মত চিকন হয়ে যাবে!
প্রশ্ন হল- এমনটা হওয়ার কারণ কি?
কারণ আর কিছুই না। কোনও পদার্থ বা মানুষের কথাই ধরুন, সে যত দ্রুত বেগে গতিশীল হবে, তার ভর কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। এবং আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে গতিশীল হলে তার ভর এতটাই বেড়ে যাবে যে, তার নিজের ভরের কারণে নিজের উপর প্রচন্ড অভিকর্ষ বলের চাপ সৃষ্টি হবে। এবং নিজের অভিকর্ষ বলের চাপের ফলে নিজেই সে সংকুচিত হতে হতে সূতার মত একসময় চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।
তারমানে আমরা যা জানতে পারলাম আপক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বানুসারে তা হল- আলোর বেগ সর্বদা একই থাকে। আলোর কাছাকাছি বেগে গতিশীল কোনও পদার্থের ভর বাড়তে থাকে, দৈর্ঘ্য সংকুচিত হতে থাকে এবং সময় দীর্ঘায়িত হতে থাকে।
আসলে সত্যি কথা হল কোনও পদার্থই আলোর বেগে চলাচল করতে পারবেনা। কারণ, সকল পদার্থ কিংবা কণারই ভর আছে। কিন্তু একমাত্র আলোর কোনও ভর নেই। যেকোনো পদার্থ কিংবা কণারই ভর থাকলে সেটা আলোর গতি অর্জনে সক্ষম হতে পারবে না। কারণ, সেটি যতই আলোর বেগের কাছাকাছি যাবে, ততই তার ভর বাড়তে থাকবে। আর ভর বাড়তে থাকলে তার গতিও কমতে থাকবে। প্রকৃতি এমনভাবে এই নিয়ম বেঁধে দিয়েছে যে আজ পর্যন্ত কারও পক্ষেই আলোর বেগের এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। তবে এমন নয় যে সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। বিজ্ঞানের তো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। কারণ বিজ্ঞান থেমে গেলে মানবসভ্যতার কি হবে? প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আর তাই বিজ্ঞানীদেরকেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য।
আলোর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য এমন নয় যে কোনও প্রতিযোগী খোঁজা হয়নি বা হচ্ছেনা। যেমন- ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুইজারল্যান্ডের সার্নে অপেরা নামক একটি প্রজেক্টের পরীক্ষায় দেখা যায় যে, নিউট্রিনো কণা আলোর বেগকে ছাড়িয়ে গেছে! গোটা পৃথিবী তখন কেঁপে উঠল এই খবরে! বিজ্ঞানীরা একেবারে শিউরে উঠলেন! কারণ, যদি সত্যিই নিউট্রিনোর বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তাহলে গোটা বিজ্ঞান জগতকে ফের নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে, যেখানে নিউট্রিনো নামক কণার মাথায় সর্বোচ্চ বেগের শিরোপা পরিয়ে দিতে হবে এবং আবার নতুন করে পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি রিমেক করতে হবে।
কিন্তু মজার ব্যাপার হল- সাধারণ মানুষ ব্যাপারটায় যতটা না পুলকিত হয়েছিল, তার চাইতে অনেক কম পুলকিত হয়েছিলেন বড় বড় পদার্থ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মোটামুটি দৃঢ়স্বরেই ঘোষণা দিলেন যে, পরীক্ষায় নিশ্চিত কোনও ত্রুটি আছে। কারণ, এর আগে নিউট্রিনোর বেগ ও আলোর বেগ নিয়ে যতটি ঘটনা ঘটেছিল, তাতে সর্বদা আলোই বিজয়ী হয়েছিল। আর তাছাড়া নিউট্রিনো কণা কিন্তু একেবারে ভরশূন্য নয়। প্রায় শূন্যের কাছাকাছি হলেও এর ভর আছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই নিউট্রিনোর পক্ষে আলোর গতিকে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মজার ব্যাপার হল- অপেরা প্রজেক্টের সাথে সংশ্লিষ্ট পদার্থবিদগণ নিজেরাও তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। আর তাদের সন্দেহ মোটেও অমূলক ছিলনা। একই পরীক্ষা যখন আবার করা হয় তখন দেখা যায় যে ঠিকই আলোর বেগ বেশি। আগের পরীক্ষার বেলায় সময় গণনার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল বলেই তারা নিউট্রিনোর গতিকে বেশি পেয়েছিলেন।
আলোর গতিকে অতিক্রম করতে পারে এমন আরেক প্রতিযোগী হচ্ছে মহাবিশ্বের স্থান বা জ্যামিতিক তল।
আমরা জানি প্রসারমান মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। এবং এই দূরে যাওয়ার গতিও বাড়ছে। সবচেয়ে দূরবর্তি গ্যালাক্সিগুলো আলোর চেয়েও বেশি বেগে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।
এখানে প্রশ্ন করা যেতে আরে যে, এত বিপুল ভরের অধিকারী একেকটি গ্যালাক্সি কি করে আলোর চেয়ে বেশি বেগে গতিশীল হবে? একটু আগেই তো আপনি বললেন যে, ভর আছে এমন কোনও পদার্থ কোনোদিনই আলোর বেগে ভ্রমণ করতে পারবেনা।
হ্যাঁ, তা ঠিক। আসলে এখানে ব্যাপার হল- এই বেগ গ্যালাক্সির বেগ নয়, স্রেফ স্থান প্রসারণের বেগ। স্থান এমন গতিতে ফুলছে যে তা আলোর গতিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে গ্যালাক্সির নিজস্ব গতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। বরং তাদের নিজস্ব ভরের ঘূর্ণন বেগ একই থাকছে। অনেকটা পুকুরের স্রোতে ছড়িয়ে পড়া অনেকগুলো ভাসমান গাছের পাতার মত। পুকুরে ভাসমান অনেকগুলো গাছের পাতা ধরুন ঢেউয়ের কারণে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এবার ধরুন, এদের মাঝখানে আপনি ঢিল ছুঁড়ে ঢেউয়ের বেগ দিলেন বাড়িয়ে। ফলে এদের ছড়িয়ে পড়ার বেগও বেড়ে গেল। আমাদেরকে কিন্তু বুঝতে হবে যে, পাতাগুলো একে অপরের কাছ থেকে দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়ছে নিজেদের বেগের কারণে নয়, বরং ঢেউয়ের বেগের কারণে। স্থানের প্রসারণের ব্যাপারটাও অনেকটা সেরকম। স্থানের বেগ আলোর বেগকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু গ্যালাক্সিগুলো নয়।
আরেকটি সম্ভাবনাময় পরীক্ষা করা হয়েছিল ইলেকট্রনকে নিয়ে। যেহেতু ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ। তাই নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রনকে ত্বরান্বিত করে হয়তো আলোর বেগ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দেখা গেল যত বেশী শক্তি দেওয়া হয় একে গতিশীল করার জন্য, এর ভরও তত বৃদ্ধি পায়। প্রথমদিকে এর গতি থাকে সর্বোচ্চ। এরপরে গতি আরেকটু কমতে থাকে। তারপর আরেকটু কমে। এভাবে দেখা যায় যে, ভরবৃদ্ধির কারণে এর বেগ ক্রমশ কমতেই থাকে। ব্যাপারটা অনেকটা ব্যাঙের লাফ দেওয়ার গানিতিক সমস্যার মত। একটি ব্যাঙ প্রথম লাফে যতটুকু যায়, দ্বিতীয় লাফে যায় তার অর্ধেক। তৃতীয় লাফে যায় দ্বিতীয় লাফেরও অর্ধেক। এই প্রক্রিয়ায় কোনও ব্যাঙ যদি তার সামনে থাকা ৫ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে চায়, তাহলে সে কি আদৌ তা অতিক্রম করতে পারবে? প্রথম লাফে যদি সে ৫/২ মিটার যায়, তো পরের লাফে সে যাবে ৫/২ মিটারেরও অর্ধেক অর্থাৎ ৫/৪ মিটার। এর পরের লাফে যায় ৫/৪ মিটারেরও অর্ধেক। এভাবে গণনা করলে দেখা যায় যে, ব্যাঙ তার সামনের ৫ মিটার দূরত্ব আসলে কোনদিনও অতিক্রম করতে পারবেনা। ইলেকট্রনের বেলায়ও অনেকটা এরকম সমস্যাই দেখা দেয়।
এবারে আরেকটি সম্ভাবনার কথা বলতে পারি আমরা। সেটাকে বলে কোয়ান্টাম ইন্টেঙ্গলমেন্ট। এটি মূলত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি তত্ত্ব। কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে একটি একটি বাস্তবতার অনেকগুলো দশা থাকে। শ্রোডিঙ্গারের বিড়ালের উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে বলা যেতে পারে। একটি বদ্ধ বাক্সে একটি বিড়াল ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে। এটি এমন একটি অবস্থায় রয়েছে যে এটি মারাও পড়তে পারে , আবার জীবিতও থাকতে পারে। যদি বাক্সের ঢাকনি খোলার আগে আপনাকে প্রশ্ন করা হয় বিড়ালটি মৃত না জীবিত? আপনি বলবেন দুটোরই সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দেখার পরে বলতে পারব জীবিত না মৃত। যখন ঢাকনি খোলা হল, ধরুন তখন দেখা গেল বিড়ালটি জীবিত। কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে বিড়ালটিকে আপনি পর্যবেক্ষন করার আগে সেটি একই সাথে জীবিত ও মৃত দুটো অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করা মাত্রই সেটি স্রেফ একটি দশায় রূপ নিয়েছে। আর অপর দশাটি সাথে সাথে অন্য কোনও সমান্তরাল মহাবিশ্বে ঘটে গেছে। অর্থাৎ আপনি যখন বিড়ালটিকে জীবিত হিসেবে দেখেছেন, মাল্টিভার্স থিওরি অনুযায়ী সাথে সাথে অন্য কোনও এক মহাবিশ্বে একই বাক্সে থাকা একই বিড়াল মারা গেছে।
মোটকথা বাস্তবতার অনেকগুলো রূপ থাকে, তবে একেক মহাবিশ্বে বা একেক স্থানে স্রেফ একেক দশা দেখা যাবে। একই সাথে আপনি দুটো দশা দেখতে পাবেন না।
এখন, একই শক্তিস্তর বা অবস্থানে ঘুরতে থাকা দুটো ইলেকট্রনের কথা যদি আমরা ধরি, তাহলে আমাদেরকে বলতে হয় যে একই অবস্থানে থাকা একজোড়া ইলেকট্রন কখনোই হুবহু একইরকম আচরণ করবেনা। তাদের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার (অবস্থান, কৌণিক ভরবেগ, চৌম্বক সংখ্যা ও স্পিন) মধ্যে অন্তত যেকোনো একটির পার্থক্য থাকবেই। যেমন- একই কক্ষপথে থাকা একজোড়া ইলেকট্রনের যদি ভরবেগ ও চৌম্বক সংখ্যা একই পাওয়া যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে যে এদের স্পিন (নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণন) ভিন্ন। এখন ধরুন, দুটো ইলেকট্রনকে আলাদা দূরত্বে নিয়ে যাওয়া হল ইচ্ছেমত। এমনকি ধরুন ১০০ আলোকবর্ষ দূরেও যদি নিয়ে যাওয়া হয় তাদেরকে, তবু তাদের এই স্পিনের পার্থক্য অব্যাহত থাকবে। এখন ১০০ আলোকবর্ষ দূরে থাকা আলাদা দুটি গ্রহে বসে দুজন বিজ্ঞানী যদি প্রত্যেকে একই সময়ে নিজের ল্যাবে থাকা ইলেকট্রনটির স্পিন মাপতে যান, দেখা যাবে যে, প্রথম ইলেকট্রনটির স্পিনের দিক যদি হয় ঘড়ির কাঁটার দিক বরাবর, তাহলে ওই একই সময়ে অন্য বিজ্ঞানী দেখবেন যে অপর ইলেকট্রনের স্পিনের দিক রয়েছে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। এবং এই দুটো ঘটনা হচ্ছে জোড় ঘটনা, অর্থাৎ একই সময়ে ঘটবে, তাদের মধ্যে দূরত্ব যতই হোক না কেন। তারমানে আমরা পেলাম যে, জোড় কণার ক্ষেত্রে এমন এক অদৃশ্য বন্ধন রয়েছে, যেখানে সময় সর্বদা একই থাকবে এবং তাদের মধ্যে যে কোনও ঘটনা বা পরিবর্তন ঘটার সময়কাল প্রায় শূন্য। অর্থাৎ আলো এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে পৌছানোর আগেই দুটি গ্রহে থাকা একজোড়া ইলেকট্রনের ঘটনা বা পরিবর্তনের গতি আলোর গতির চেয়েও বেশি। কিন্তু সমস্যা হল- যে দুজন বিজ্ঞানী দুই গ্রহে থেকে এই দুই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁরা পরস্পরকে নিজেদের প্রাপ্ত এই ফলাফল জানাতে গেলে যখন যোগাযোগ করতে যাবেন, সেই যোগাযোগকালের মধ্যেই আলো সেখানে পৌছে যাবে! কারণ, ১ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে থাকুন আর ১ মাইল দূরে থাকুন না কেন, একটা বাটন চেপে যোগাযোগ করতে গেলেও আলো আপনাদের দুজনের অবস্থানকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে! অর্থাৎ আলোকে ফাঁকি দিয়ে আলোর চাইতে বেশি বেগে ঘটা কোনও ঘটনা আপনি আলো পৌছানোর আগে কাউকে জানাতেও পারবেন না। হার আপনাকে মানতেই হবে।
আলোর চেয়ে অধিক বেগ অর্জনের আরেকটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ার্মহোল এর ভেতর দিয়ে পরিভ্রমণ করা। ওয়ার্মহোল হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা বা ছিদ্রপথ, যা দ্বারা দুটি ভিন্ন মহাবিশ্বের স্থানের মধ্যে সংযোগ দেওয়া যাবে। আমরা জানি যে, ব্ল্যাকহোলের ভেতর কোনও বস্তু পতিত হলে সেটি আর ফিরে আসতে পারেনা তার অসীম মধ্যাকর্ষণের কারণে। কিন্তু ওয়ার্মহোল হচ্ছে ব্ল্যাকহোলের মতই মধ্যাকর্ষণ শক্তির অধিকারী দ্বিমুখী ছিদ্রপথ, যার ভেতর দিয়ে কোনও বস্তু যেতেও পারবে, আবার ফিরেও আসতে পারবে। কিন্তু দুটো স্থানের মধ্যে এমন সংযোগ দেওয়া কি আদৌ সম্ভব?
বিজ্ঞানীরা বলছেন বিপুল পরিমাণ শক্তির অধিকারী কোনও লেজার রশ্মি দিয়ে মহাশূন্যের কোনও স্থানের জ্যামিতিক তল ছিদ্র করে হয়তবা তা করা সম্ভব। কিন্তু ওই বিপুল পরিমাণ শক্তি বলতে ঠিক কি পরিমাণ শক্তি তাঁরা বুঝিয়েছেন? একটি কৃত্রিম ওয়ার্মহোল তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করলেই বুঝা যাবে যে ওয়ার্মহোল তৈরি করতে কি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। ওয়ার্মহোল তৈরি করতে হলে পজেটিভ ও নেগেটিভ- এই দুই প্রকারের শক্তিই আমাদের প্রয়োজন। দুই প্রকারের শক্তি থাকার কারণে আমরা তার ভেতর দিয়ে যেমন গমন করতে পারব, তেমনি ফিরেও আসতে পারব। আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব পজিটিভ এনার্জি দ্বারা গঠিত। এখন সমস্যা হল- নেগেটিভ এনার্জি আমরা পাব কোথায়? উত্তর হল- তৈরি করতে হবে। কিন্তু কিভাবে?
১৯৩৩ সালে হেনরিখ কাসিমির একটি তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে, দুটো চার্জবিহীন ধাতব পাতকে খুব কাছাকাছি অনেকক্ষণ ধরে রাখলে তারা একসময় পরস্পরকে আকর্ষণ করবে। এর কারণ হল, তাদের মাঝখানে যে সামান্য ব্যবধান রয়েছে, সেই স্থানে স্বল্প সংখ্যক নেগেটিভ কণার সৃষ্টি হবে স্বল্প সময়ের জন্য। এতে শক্তির সংরক্ষণ নীতি কিন্তু অমান্য হয় না। খুব স্বল্প সময়ের জন্য শূন্যতার মধ্যে নেগেটিভ ও পজেটিভ কণা (যেমন- ইলেকট্রন ও পজিট্রন) দেখা দিয়েই আবার শূন্যতায় মিলিয়ে যায়। এমনকি এরা টিকে গেলেও সমস্যা নেই। কারণ, মোট নেগেটিভ ও পজেটিভ কণার যোগফল তো শূন্য। তাই ধাতবপাত দুটোর মধ্যে থাকা ওই হালকা দূরত্বে অল্প সময়ের জন্য নেগেটিভ ও পজেটিভ এনার্জির সৃষ্টি হয়। আর মাঝখানে বাতাসের চাপ খুব কম থাকায় সেই শক্তি কার্যকরি হয়ে ওঠে। ফলে ধাতব প্লেট দুটো পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আবার প্লেট দুটোকে দূরে রাখলে এমনটি ঘটবে না। কারণ, এত দূর থেকে সামান্য নেগেটিভ ও পজেটিভ শক্তির আকর্ষণ শক্তি বাতাসের বিশাল পরিমাণ চাপকে অগ্রাহ্য করে কার্যকর হতে পারবে না।
কাসিমিরের এই তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালে ঠিকই প্রমাণিত হল। শূন্যস্থানে প্লাংক দূরত্বের মধ্যে অতি অল্প সময়ের জন্য পজিটিভ ও নেগেটিভ কণা দেখা দিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এই প্লাংক স্কেলের মধ্যে ঘটা কোনও পজিটিভ নেগেটিভ কণার উৎপত্তি হয়ে যদি তাদের মহাস্ফীতি ঘটে, তাহলে হয়তো গোটা একটা মহাবিশ্বও তৈরি হয়ে যেতে পারে। এ ধারণা থেকেই মূলত বিগ-ব্যাং তত্ত্বের কসমিক ইনফ্লেশন মডেলের ধারণা পাওয়া গেছে।
যাই হোক। নেগেটিভ এনার্জির বৈশিষ্ট্য হল এর সবকিছুই হচ্ছে পজেটিভ এনার্জির উল্টো। পজেটিভ কণার চার্জ ও ভরের ঠিক উল্টো হচ্ছে নেগেটিভ কণার চার্জ ও ভর। তাই নেগেটিভ শক্তি দ্বারা তৈরি কোনও মহাবিশ্ব থাকলে সেটি হবে আমাদের ঠিক উল্টো মহাবিশ্ব। আপনি আয়নায় যেমন নিজের উল্টো ছবি দেখেন ঠিক তেমনি নেগেটিভ মহাবিশ্বে আপনার উল্টো আরেক অস্তিত্ব (মানে ডানপাশ আপনার বামদিক ও বামপাশ আপনার ডানদিকে থাকবে) থাকবে, যার হার্ট থাকবে ডানপাশে। তাই ওয়ার্মহোল তৈরি করতে গেলে নেগেটিভ এনার্জি লাগবে।
কিন্তু ল্যাবেরটরিতে বিজ্ঞানীরা যে সামান্য পরিমাণ নেগেটিভ কণা তৈরি করতে পারেন, তা খুবই নগণ্য! একটি ১ মিটার লম্বা দৈর্ঘ্যের ওয়ার্মহোল তৈরি করতে গেলে যে পরিমাণ নেগেটিভ কণার দরকার, সেই পরিমাণ পজিটিভ কণা দিয়ে বৃহস্পতি গ্রহের সমান আস্ত একটি গ্রহ তৈরি করে ফেলা যাবে! আর ওই পরিমাণ নেগেটিভ শক্তি তৈরি করার কথা আমরা বাস্তবে কল্পনাও করতে পারিনা! আর তারচেয়েও বড় ব্যাপার হল মানুষ আসা যাওয়া করতে পারে, এমন একটি বড় মাপের ওয়ার্মহোল তৈরি করতে যে পরিমাণ নেগেটিভ এনার্জির দরকার তা আসলে মানবসভ্যতার কল্পনারও বাইরে। আর তাছাড়া শুধু ওয়ার্মহোল তৈরি করলেই তো আর কিচ্ছা খতম হয়ে যাবে না। আরও সমস্যা আছে।
ওয়ার্মহোলের মধ্যে যে পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শক্তির রেডিয়েশন হবে, তাতে মানুষ মারাও পড়তে পারে। আর তাছাড়া, ওয়ার্মহোলটি টিকবে কতক্ষণ সে সম্পর্কেও মানুষের কোনও ধারণা নেই। যদি একটি নক্ষত্রের ভরের সমপরিমাণ শক্তি দিয়ে একটি ছোটখাটো ওয়ার্মহোল তৈরি করা যায়, আর সেটার ভেতর কেউ ঢোকার সাথে সাথেই যদি সেটি অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে সব পরিশ্রম একেবারে মাঠে মারা যাবে।
স্রেফ একটা কাজ করা যায় ওয়ার্মহোল তৈরির জন্য, সেটা হচ্ছে এমন কোনও সুপারব্যাটারি আবিষ্কার করা যা দিয়ে মারাত্মক শক্তিশালী লেজার রশ্মি নির্গমন করে মহাশূন্যের স্থানের মধ্যে ছিদ্র করে তার ভেতর দিয়ে অন্যস্থানে চলে যাওয়া, ঠিক যেরকম ধারণা করা হয় যে ব্ল্যাকহোলের রাস্তা গিয়ে অন্য স্থানে বা অন্য মহাবিশ্বে যুক্ত হয়েছে সেরকম। কিন্তু আদৌ কি ওই ধরণের শক্তিশালী লেজার তৈরির জন্য ওরকম শক্তিশালী সুপার পাওয়ারের ব্যাটারি তৈরি করা সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবে কেবল তখনই আমরা ওয়ার্মহোল তৈরি করতে পারব, যার ভেতর দিয়ে শর্টকাটে আমরা আলো পৌছানোর আগেই অন্য স্থানে পৌছে যেতে পারব আলোর চেয়ে বেশি বেগে। কারণ, ওয়ার্মহোলের দুই স্থানের সময়ের ব্যবধান যত বেশীই হোক, সেটা কোনও সমস্যা নয়। যে স্থানে আলো এখনও পৌঁছায়নি, সেখানেও আপনি ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে শর্টকার্টে চলে যেতে পারবেন। কিন্তু আমরা আজও জানিনা ওয়ার্মহোল তৈরির সম্ভাব্য উপায়টা কি।
আলোর চেয়ে বেশি বেগে পরিভ্রমণ করার আরেকটি সম্ভাব্য রাস্তা হচ্ছে, স্থান-কালের আগে গিয়ে স্থানের বেগের দ্বারা নিজেকে বা নিজের শীপকে পরিচালনা করা বা সার্ফিং করা। সমুদ্রে যেরকম মানুষ সার্ফিং বোর্ডে চেপে ঢেউয়ের উপর উঠে তারপর ঢেউয়ের ধাক্কাকে কাজে লাগিয়ে ঢেউয়ের আগেই তীরে পৌঁছায়, ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম। যেহেতু স্থান আলোর চেয়েও বেশি বেগে প্রসারিত হয়, তাই যেকোনোভাবে আপনাকে এমন স্থানে পৌঁছাতে হবে যেখানে প্রসারণের গতি আলোর চেয়ে বেশী। তারপর আপনি সেই স্থানের প্রসারণের ধাক্কাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাবেন, অথবা স্থানের ঢেউকে ব্যবহার করে আপনি কোনও শীপে চেপে সার্ফিং করতে পারবেন আলোর চেয়েও বেশি বেগে। অনেকটা গ্যালাক্সির প্রসারণের মত। গ্যালাক্সিগুলো যেভাবে একটির থেকে অপরটি স্থানের বেগের উপর চেপে আলোর চেয়ে দ্রুত বেগে দূরে সরে যাচ্ছে, ঠিক সেভাবে মানুষ কোনও শীপ নিয়ে প্রসারণের ওই স্থানে পৌঁছাতে পারলে হয়ত স্থানের ধাক্কাকে কাজে লাগিয়ে আলোর চেয়ে বেশি বেগে যাত্রা করতে পারবে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল- এমন দ্রুত বেগের স্থানে আপনি কিভাবে পৌছাবেন যেখানে আলোর গতিও হেরে যায়?
তাই উপরের সমস্ত আলোচনা শেষে আমরা উপসংহারে এসে বলতে পারি যে, আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব দ্বারা আলোর মাথায় এমন এক শিরোপা পড়িয়ে গেছেন, যেটা তার মাথা থেকে নামানোর মত যোগ্যতা অন্য কোনও কিছুর পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব হয়নি। আলো বা ফোটন হচ্ছে জন্মগতভাবেই ভরশূন্য। তাই তাকে ভর কমিয়ে বেগ অর্জন করার মত কোনও সমস্যায় কখনও পড়তে হয়না। যার ভরই নেই, তার আবার ভর কমানোর চিন্তা থাকবে কি করে? তাই আলোর বেগ আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ বেগ, যা কোনও পদার্থ বা কণার পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব হয় না।
দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ কিংবা কণা এমন এক মহাজাগতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় রয়েছে, যেখানে আলোই বরাবর গোল্ড মেডেল পেয়ে যাচ্ছে। তার সমকক্ষ বাস্তব, দৃশ্যমান কোনও প্রতিযোগীকে আজও আমরা খুঁজে পাইনি। আর যেসমস্ত প্রযুক্তির কথা ভাবা হয় যা আলোর বেগকে অতিক্রান্ত করতে পারবে, তার সবগুলোই এখন পর্যন্ত তাত্ত্বিক, যার কোনোটাই আদৌ কোনোকালে তৈরি করা সম্ভব হবে কিনা তা কেউ জানেনা। আর যা কিছু আলোর চেয়ে বেশি বেগে ধাবমান, যেমন স্থানের প্রসারণের বেগ, তা আমাদের পর্যবেক্ষণের বাইরে। অর্থাৎ আলোকে যদি দৌড় প্রতিযোগিতায় কেউ কখনও হারাতে পারে, সেটা আমরা কোনোকালেই দেখতে বা পর্যবেক্ষণ করতে পারব না। কারণ, যেখানে এখনও আলোই পৌছেনি, সেখানে আপনার দৃষ্টিশক্তি পৌছাবে কি করে?
[বিঃদ্রঃ লেখাটি ২০১৮ সালে বইমেলায় প্রকাশিত আমার বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিস্ময়'- থেকে প্রকাশ করা হল। -অনন্ত নিগার]



 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।