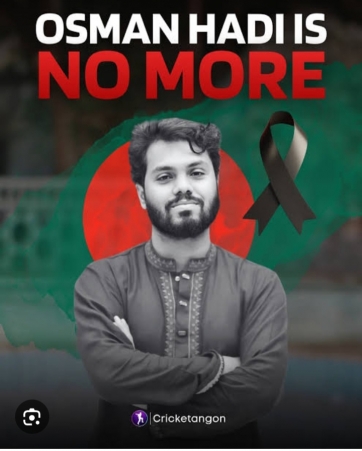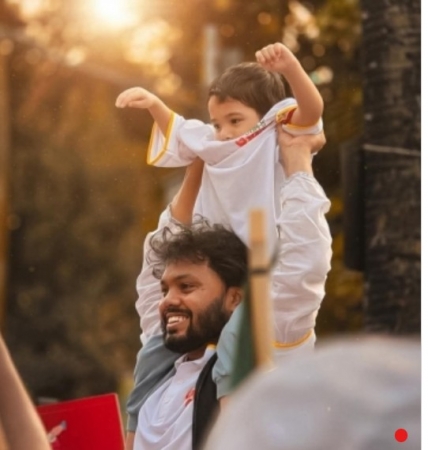'ন' এবং 'ণ' এর পার্থক্য ও প্রয়োগ; বাংলা ব্যাকরণের এই জটিল জিনিষের প্রায়োগিক ব্যবহারকে যেভাবে পানির মত সহজে আয়ত্বে নেয়া সম্ভব

ছেলেবেলায় অর্থাৎ, একাডেমিক জীবনে 'ন' এবং 'ণ' এর পার্থক্য ও প্রয়োগ পাঠের মুখোমুখি হননি, বাংলা শিক্ষিত এমন মানুষ সম্ভবতঃ তেমন একটা পাওয়া যাবে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাস, সন্ধি বিচ্ছেদ বা কারকের চেয়েও এই জিনিষকে ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান নামে আরও জটিলভাবে উপস্থাপন করার ফলে আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে এগুলোকে কঠিন কিছুর পাঠ মনে হয়েছে। অতএব, সমাধান একটাই, গোজামিল দিয়ে কোনরকমে চালিয়ে যাওয়া অথবা, বুঝার চেষ্টায় না গিয়ে গতবাধা কিছু জিনিষ মুখস্ত করে শুধু ক্লাশ ডিঙ্গিয়ে পরের ক্লাশে উন্নীত হওয়ার চেষ্টায় গলদঘর্ম হওয়া। অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধানের আলোচনা এলে অনেকেরই গায়ে জ্বর ওঠার দশা সচরাচরই দেখা যেত। এই সময়ে এসেও সেই চিরচেনা চিত্র যে খুব একটা পাল্টেছে, তা বলার সময় সম্ভবতঃ এখনও আসেনি।
আচ্ছা, ভয়ের কিছু নেই, ণ-ত্ব বিধান নিয়ে জটিল জটিল শব্দ ও কথায় জ্ঞানগর্ভ দীর্ঘ আলোচনায় যাওয়ার ইচ্ছে এই লেখায় মোটেই নেই। বরং যতটা সংক্ষেপে পারা যায় চেষ্টা করা হবে, বিষয়টিকে সংক্ষেপে বোধগম্যাকারে ফুটিয়ে তুলতে। তবে 'ন' এবং 'ণ' এর পার্থক্য ও প্রয়োগের বিষয়টি ভালভাবে বুঝার সুবিধার্থে বাংলা ভাষার শব্দ প্রকরণেও মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেই আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ এই মুহূর্তে না থাকলেও অতি সংক্ষেপে এখানে আমরা তৎসম এবং তদ্ভব শব্দ সম্মন্ধে একটু সাধারণ ধারণা নিতে সচেষ্ট হবো এবং এরপরেই মূল আলোচনায় প্রবেশ করবো ইনশাআল্লাহ। কারণ, এই তৎসম এবং তদ্ভব শব্দ সম্মন্ধে সাধারণ একটি ধারণা না থাকলে, আরও ক্লিয়ার করে বললে তৎসম এবং তদ্ভব শব্দ কোনগুলো তা চিহ্নিত করার যোগ্যতা না থাকলে 'ন' এবং 'ণ' এর পার্থক্য ও প্রয়োগের ব্যাপারটা বুঝতে কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে। সেই কারণে চলুন, প্রথমেই একে একে জেনে নেয়া যাক তৎসম এবং তদ্ভব শব্দের পরিচয়।
তৎসম শব্দ কাকে বলে?
তৎসম শব্দটির অর্থ: "তার সমান"। প্রশ্ন আসতে পারে যে, 'তার সমান' মানে কী? এখানে 'তার' কথাটা দিয়ে কী বুঝানো হল? এর উত্তর হচ্ছে, আধুনিক বাংলা, মারাঠি, ওড়িয়া, হিন্দি, গুজরাটি ও সিংহলীর মতো ইন্দো-আর্য ভাষায় এবং মালায়ালম, কন্নড, তেলুগু ও তামিলের মতো দ্রাবিড় ভাষাসমূহে সংস্কৃত ভাষা থেকে ঋণকৃত শব্দসমূহকে বোঝায়। এসব সাধারণত প্রচলিত শব্দের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিকতর চলনসই স্বরভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে অনেকগুলিই (আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষায়) পুরানো ইন্দো-আর্য (তদ্ভব) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। তৎসমের শব্দভাণ্ডারকে ইংরেজিতে গ্রিক বা লাতিন উৎস থেকে ধারকৃত শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।
কিছু তৎসম শব্দঃ
পন্থা, শুষ্ক, পুরস্কার, আদেশ, অনুরোধ, অনুবাদ, উদ্ধার, উন্নত, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, ইতিহাস, কর্ণ, চক্ষু, ভারতবর্ষ, রাষ্ট্র, মস্তক, হস্ত, উদর, জঠর, রাম, রাবণ, পুত্র, মাতা, পিতা, জননী, পক্ষী, নীড়, নীর, দীর্ঘ, বাতায়ন, ভূমিকা, উচ্চ, নিম্ন, আদেশ, বর্জন, সূর্য, চন্দ্র, জল, গৃহ, মৃত্তিকা, অলক, মর্ত্য, স্বর্গ, লোভ, সাধু, ঋষি, প্রত্যাঘাত, কর্ষণ, বর্ষণ, বৃষ্টি, কণা, বাণী, বণিক, লৌহ, বীণা, রুদ্র, চণ্ডাল, কৃষক, দিবা, সৌর্য, বীর্য, কৃতিত্ব, আদিত্য, নারায়ণ, দেব, দেবী, দর্শন, বয়ন, গমন, রাত্রি, মুষ্ঠি, কপাল, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা, আকর, সমুদ্র, নদী, মেঘ, লোক, রাজ্য, রাজধানী, এক, দশ, উদ্যান, রাজা, রাণী, রাজপুত্র, বৃক্ষ, পশু, লতা, নর, নারী, বেদ।
তদ্ভব শব্দ কাকে বলে?
যেসব শব্দের মূল পাওয়া গিয়েছে সংস্কৃততে এবং সংস্কৃত থেকে প্রাকৃততে এবং প্রাকৃত থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে। তদ্ভব শব্দের অপর নাম খাঁটি বাংলা শব্দ।
তদ্ভব শব্দের কয়েকটি উদাহরণ-
সংস্কৃত -----< প্রাকৃত >----- তদ্ভব
মৎস--------------- মচ্ছ------------ মাছ
হস্ত --------------- হত্থ ----------- হাত
চন্দ্র -----------------চন্দ----------- চাঁদ
কর্মকার-------------কম্মআর-------কামার
দুগ্ধ------------------দুদ্ধ-----------দুধ
চর্মকার--------------চম্মআর-------চামার
'ন' এবং 'ণ' -এর উচ্চারণ ও পরিচয়ঃ
আমরা 'ন'-কে 'দন্ত্য ন' এবং 'ণ'-কে 'মূর্ধন্য ণ' বলে ডাকি। ডাকবো না তো কী করবো? এগুলোর নামই তো এমন। জ্বি, প্রশ্ন সেই নামকরণ নিয়েই। এই অক্ষরগুলোর এমন নাম কেন হলো? তারপরেও কথা রয়ে যায়, 'দন্ত্য' এবং 'মূর্ধন্য' শুধু কি এই দু'টি অক্ষরের নামের ক্ষেত্রেই? তাও তো নয়। 'দন্ত্য স' এবং 'মূর্ধন্য ষ'ও তো রয়েছে। কথা হচ্ছে, বাকি অক্ষরগুলোর নামের সাথে এইজাতীয় বিশেষণ না থাকলেও এগুলোতে কেন আমরা তা ব্যবহার করতে গেলাম?
এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, এর কারণ একটাই, পার্থক্য করার জন্য। আমরা 'ত'-কে তো আর 'দন্ত্য ত' বলি না, আর 'ট'-কেও 'মূর্ধন্য ট' নামে অভিহিত করি না। কারণ বাংলার ধ্বনিবিজ্ঞান অনুযায়ী দু'টোর উচ্চারণ দিয়েই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে যায়। তবু বাংলায় 'ন' এবং 'ণ'-তে উচ্চারণগত তেমন কোনো পার্থক্য নেই।
ধ্বনিতত্ত্বে 'ণ'-এর পোশাকি নাম মূর্ধন্য নাসিক্যধ্বনি (Retroflex Nasal); আর 'ন'-এর দন্তমূলীয় নাসিক্যধ্বনি (Alveolar Nasal)।
লক্ষনীয় যে, বাংলা ভাষায় বর্ণমালার ক্রমধারায় মূর্ধন্য-ণ -এর অবস্থান ‘ট, ঠ, ড, ঢ’ -এই চারটি বর্ণের পরে। এই বর্ণ চারটি উচ্চারণ করতে গিয়ে নিশ্চয়ই একটি সাদৃশ্য বা সাযুজ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এই চারটি বর্ণের প্রতিটির উচ্চারণেই জিহবার অগ্রভাগটা উল্টে গিয়ে উপরের (মূর্ধা) অংশে ঠিক যেন একটি টোকা দেয়। আবার, দন্ত্য-ন-এর আগে আসে ‘ত, থ, দ, ধ’। এদের উচ্চারণও একইরকম। এক্ষেত্রে জিহবা দাঁতের গোড়ালির দিকের পেছনের অংশটা ছুঁয়ে যায়। অর্থাৎ ‘ণ’ আর ‘ন’ এর উচ্চারণেও তাদের সঙ্গীদের সঙ্গে মিল থাকা উচিত।
শুধু ‘ট, ঠ, ড, ঢ’-এর সাথে যুক্ত হয়ে থাকা (ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ) ছাড়া বাংলায় মূর্ধন্য-ণ -এর উচ্চারণ লুপ্ত হয়ে সবই দন্ত্য-ন হয়ে গেছে, বরং বলা ভালো, দন্তমূলীয়-ন হয়ে গেছে। কারণ ‘ন’ একা থাকলে যেটা উচ্চারণ করি, সেটা দাঁত না ছুঁয়ে দাঁতের শুধু গোড়াটা ছোঁয়। কিন্তু ‘ত, থ, দ, ধ’-এর সাথে যুক্ত থাকলে তখন বিষয়টা হয়ে যায় আলাদা। ‘অন্ত’ আর ‘অন্য’ উচ্চারণ করলেই পার্থক্যটা বুঝা সম্ভব।
'ন' এবং 'ণ' -এর পার্থক্য ও প্রয়োগঃ
তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ ধ্বনির সঠিক ব্যবহারের নিয়মকে ণ-ত্ব বিধান বলে। অর্থাৎ যে নিয়মে দন্ত্য ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’ -তে পরিণত হয়, তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে। বাংলা ভাষায় শুধুমাত্র তৎসম শব্দে ণ-ত্ব বিধান কার্যকরী।
তদ্ভব, খাঁটি বাংলা শব্দ বা দেশি এবং বিদেশি শব্দে ণত্ব বিধান সাধারণত গ্রহণযোগ্য নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, যে নিয়মে দন্ত্য ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’-তে পরিণত হয়, তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে।
++ ছোটবেলায় পণ্ডিত মশাইয়ের শেখানো দুই লাইনের সেই কাব্যকথা কিন্তু ণ-ত্ব বিধানের মজার একটি নিয়ম মনে রাখার জন্য বেশ সহায়ক। কয়েকবার পড়ুন এবং এখনই মুখস্ত ও ঠোটস্থ করে নিতে পারেন নিচের লাইন দু'টি। পণ্ডিত মশাই শিখিয়েছিলেন-
"ঋ-কার, র-কার, ষ-কারের পরে, যদি ন-কার থাকে,
ঘ্যাচ্ করে তার কেটে দাও মাথা, কোন্ বাপ্ তারে রাখে"।
সেটাই, শুধু মাথাটা কেটে দেয়াই কাজ। ব্যস, প্রয়োগ হয়ে যাবে ণ-ত্ব বিধান -এর। অর্থাৎ ঋ -কার, র -কার অর্থাৎ র - ফলা বা রেফ্, এবং ষ থাকলে, সেসব ক্ষেত্রে অবশ্যই ণ হবে, ন নয়। চলুন, উদাহরণ দেখে বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করি। যেমন- ঋণ, ঘৃণা, তৃণ, রণ, ব্রণ, কর্ণ, ঘ্রাণ, বর্ণ, বর্ণনা, কারণ, মরণ, ভীষণ, ভাষণ, বিভীষণ, ভূষণ, উষ্ণ, পাষাণ ইত্যাদি।
'ন' এবং 'ণ' -এর আরও কিছু প্রয়োগক্ষেত্রঃ
++ ট-বর্গীয় (ট, ঠ, ড, ড়, ণ) ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সবসময় মূর্ধন্য ‘ণ’ যুক্ত হয়। যেমন– ঘণ্টা, লুণ্ঠন, কাণ্ড, ইত্যাদি।
++ উপসর্গ (প্র, পরা, পরি, নির) -এর পর মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়। যেমন– প্রমাণ, নির্ণয়, পরিমাণ, প্রচণ্ড, পরাণ।
++ ঋ, র, য -এর পরে স্বরধ্বনি, ক-বর্গীয়, প-বর্গীয় (প,ফ, ব, ভ, ম,) এবং (য য় ব হ ং) ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন– কৃপণ, অর্পণ, দর্পন, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।
++ কিছু সন্ধি সাধিত শব্দে (উত্তর, পর, পার, চন্দ্রা, নার)- ইত্যাদির পরে ‘অয়ন’ /আয়ন’ শব্দ হলে দন্ত্য- ন মূর্ধন্য- ণ তে রুপান্তর হয়। যেমন উত্তর+আয়ন = উত্তরায়ণ, পর+আয়ন = পরায়ণ, চন্দ্রা+আয়ন = চন্দ্রায়ণ, নার+আয়ন = নারায়ণ ইত্যাদি।
++ সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ‘ন’ হয়। যেমন – ত্রিনয়ন (তিন নয়ন), সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক।
++ ত-বর্গীয় (ত, থ, দ, ধ, ন) বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনাে ণ হয় না, ন হয়। যেমন গ্রন্থ, ক্রন্দন, বন্ধন, রন্ধন।
লেখাটি প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা উইকিপিডিয়া, কোরাসহ অন্যান্য উৎসের প্রতি।
সাথে থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।
চলবে....।
সর্বশেষ এডিট : ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০২২ দুপুর ২:০০


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।