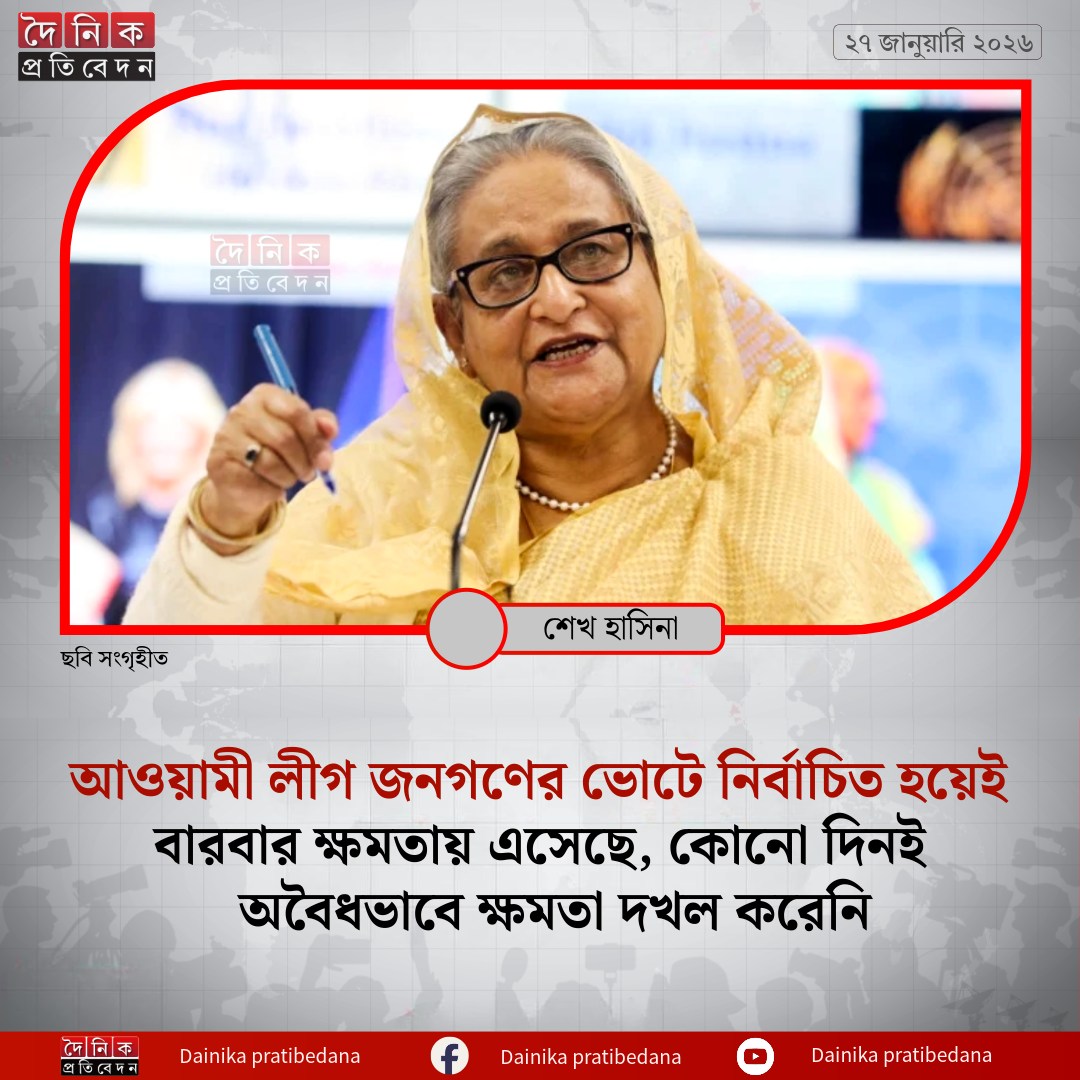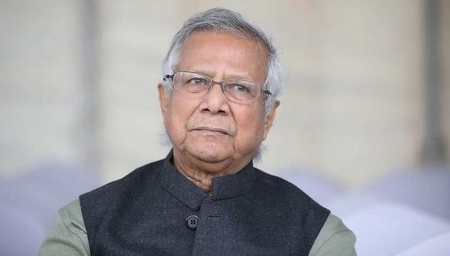আমার শৈশবের স্মৃতিচারণে রেল যাত্রার কথা ঘুরে ফিরে আসে। শৈশব-কৈশোর-যৌবন পর্যন্ত আমাদের ঢাকা থেকে দাদাবাড়ি-নানাবাড়ি যাওয়া মানেই ছিল 'রেল যাত্রা'। তখন ঢাকা থেকে সাধারণতঃ দুটো ট্রেন এ্যাভেইলেবল ছিল। সকাল ৮ টার ১১ আপ "দ্রুতযান এক্সপ্রেস" আর রাত ১১ টার ৭ আপ "নর্থ বেঙ্গল মেইল। ০১ মে ১৯৬৮ তারিখে কমলাপুর রেল স্টেশনটি উদ্বোধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ট্রেনগুলো যাত্রারম্ভ করতো নারায়ণগঞ্জ থেকে, ঢাকায় থামতো গুলিস্তানের নিকটস্থ "ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে। তখন ঢাকা ছিল প্রারম্ভিক কোন স্টেশন নয়, শুধুমাত্র ‘চলতি পথের একটি স্টেশন’ মাত্র। সেই ফুলবাড়িয়া স্টেশন থেকে শেষ ট্রেনটি ছেড়ে যায় ৩০ এপ্রিল ১৯৬৮ সালে। আমরা উঠতাম সেখান থেকেই, ১২ ঘণ্টার জার্নী শেষ করে যেতাম সুদূর লালমনিরহাট জংশনে। তখন ও দুটো দ্রুতগামী ট্রেনের কোনটাই লালমনিরহাট পর্যন্ত যেত না। 'কাউনিয়া' নামক স্টেশন থেকে ওগুলো ইঞ্জিন ঘুরিয়ে সরাসরি রংপুর-পার্বতীপুর-দিনাজপুর চলে যেত। আমরা কাউনিয়ায় নেমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লোকাল কানেক্টিং ট্রেন ধরে বাকি তিনটা স্টেশন অতিক্রম করে লালমনিরহাট যেতাম। অবশ্য তখন আমাদের কাছে এতদূর ক্লান্তিকর জার্নী করে এসে ঐ ছোট্ট তিনটে লোকাল স্টেশন অতিক্রম করাকেই পাহাড়সম ভারময় মনে হতো।
তখন রেলপথে উত্তরবঙ্গবাসীদেরকে এবং বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমের ও দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোর যাত্রীদের পারাপারে ময়মনসিংহ জংশন এক বিরাট কর্মযজ্ঞ পালন করতো। বিশেষ করে রাতের মেল ট্রেনগুলোতে এ ঘটনাগুলো ঘটতো। এত বিশাল কর্মযজ্ঞ কিভাবে তখনকার রেল-কর্মচারীগণ সামলাতেন, সেটা এখন ভাবাও যায় না। আমরা উত্তরবঙ্গবাসীরা যেমন ঢাকা থেকে রাত এগারটার নর্থ বেঙ্গল মেইলে রওনা দিতাম, চট্টগ্রাম থেকেও তেমনি উত্তরবঙ্গবাসীরা রাত নয়টার একটা মেল ট্রেনে রওনা দিত। বোধকরি, সেটার নামও ছিল ‘নর্থ বেঙ্গল মেইল’। রাত দুইটা -আড়াইটার দিকে উভয় ট্রেন এসে মিলিত হতো ময়মনসিংহ জংশনে। সেখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলতো ট্রেনের বগী কাটাকাটি করে দুটো পৃথক রুটে যাবার জন্য দুটো পৃথক ট্রেন সেট করার কাজ। বেশিরভাগ যাত্রী এসব টের পেতেন না, কারণ তখন মধ্যরাত থাকতো এবং যাত্রীরা ঘুমিয়ে থাকতেন।
ময়মনসিংহ থেকে একটা ট্রেন জামালপুর-ইসলামপুর হয়ে বাহাদুরাবাদঘাট চলে যেত। সেখানে ট্রেন থেকে নেমে প্রায় ৭০০/৮০০ মিটার পথ বোঁচকা-বাচকিসহ পায়ে হেঁটে ফেরিতে উঠতে হতো। হাঁটার দূরত্বটার তারতম্য ঘটতো সীজন অনুযায়ী। বর্ষাকালে নদী ভাঙতো, ফলে কাঁচা মাটির উপর রেল বসিয়ে নতুন পথ তৈরি করা হতো, ফেরিঘাটও সুবিধামত জায়গায় স্থানান্তর করা হতো। ফলে দূরত্ব বেড়ে যেত। শীতকালে মাটি শক্ত থাকতো বিধায় ট্রেনটি যথাসম্ভব ফেরিঘাটের কাছাকাছি গিয়ে থামতো। ট্রেন থামার জায়গা থেকে ফেরিঘাট পর্যন্ত পথের দু’পাশে সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলো কাঁচা হোটেল থাকতো। হোটেলের কর্মচারীরা তাদের হোটেলে খেয়ে যাবার জন্য যাত্রীদের উদ্দেশ্যে গলা ফাটিয়ে হাঁকডাক করতো। আমার মনে পড়ে, একটা হোটেল ছিল “কলিম মিঞার হোটেল” নামে। সেটা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। তবে আমি কখনো সেখানে খাইনি। আমার কাছে স্টীমারের খাবারই উত্তম মনে হতো। বিশেষ করে লাঞ্চের পরে তাদের দেয়া পুডিংটা ছিল খুবই সুস্বাদু।
স্টীমার গিয়ে ভিড়তো তিস্তামুখঘাটে। ঘাটটি একসময় ফুলছড়িঘাট নামে সুবিদিত ছিল। কিন্তু একদা মর্মান্তিকভাবে অকস্মাৎ নদীগর্ভে বিলীন হবার পর নতুন একটি ঘাট নির্মাণ করা হয়, সেটির নাম দেয়া হয় ‘তিস্তামুখঘাট’। ঘাটে ফেরি লাগার সাথে সাথে শুরু হয়ে যেত কুলিদের দৌরাত্ম্য। ওরা যাত্রীদের মালামাল নিয়ে টানাটানি করতো। যাত্রীদের মধ্যে যারা হাল্কা মালামাল নিয়ে ভ্রমণ করতেন, তারা নিজেদের মাল নিজেরাই নিয়ে পরবর্তী ট্রেনের উদ্দেশ্যে ছুটতেন। যাদের কাছে ভারী মালামাল থাকতো, তাদের কুলিদের ইচ্ছের কাছে নিজেদের সমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকতো না। যদিও কুলিদের এ কাজটাকে আমি ‘দৌরাত্ম্য’ বলেছি, কিন্তু এতে আমার মন থেকে কখনোই সায় পাই না। ওদের জায়গায় যদি আমি থাকতাম, আমিও ঠিক একই কাজটি করতাম। ওরা নদী সিকস্তি মানুষ। ওদের স্থায়ী কোন ঘরবাড়ি নেই। আজ এখানে ঘর ভাঙে তো কাল সে ওখানে গড়ে। সারাদিনে ওদের আয় রোজগারের পথ ও পন্থা দৈনিক ঐ দু’টি ট্রেনের যাত্রীদের মালামাল ফেরিতে তোলা ও নামানো থেকে। আমি যখন সম্ভবতঃ দশম শ্রেণির ছাত্র, তখন আমাদের পাঠ্যপুস্তকে মিরজা আব্দুল হাই রচিত “ওরা মরেনা” শীর্ষক একটি চমৎকার ছোটগল্প ছিল। ঐ গল্পটা পড়ে আমার ওদের উপর ভীষণ রকমের একটা মায়া জন্মেছিল।
তিস্তামুখঘাট ছেড়ে ভরতখালী হয়ে ট্রেনটি যেত বোনারপাড়া জংশনে। সেখানে বিরাট লম্বা ট্রেনটি আবার দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যেত। সামনের অংশটি যেত শান্তাহার হয়ে নাটোর-নওগাঁ-রাজশাহীর দিকে, আর পেছনের অংশের যাত্রীরা যেত গাইবান্ধা, কাউনিয়া,রংপুর, পার্বতীপুর ও দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে। ময়মনসিংহে ভাগ হওয়া অপর ট্রেনটি যেত জামালপুর-সরিষাবাড়ি হয়ে জগন্নাথগনঞ্জ ঘাটে। একই পন্থায় ফেরি পার হয়ে সে ট্রেনের যাত্রীরা পৌঁছে যেতেন সিরাজগঞ্জ ঘাটে। সেখানে অপেক্ষমান ট্রেনে চেপে তারা চলে যেতেন পাবনা, ঈশ্বরদী, যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনার দিকে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের রোড নেটওয়ার্ক এর প্রভূত উন্নতি সাধন হবার ফলে এখনকার দিনের বাসে বা সড়কপথে চলাচলকারী যাত্রীরা কল্পনাও করতে পারবে না যে একসময় ঐসব দূর দূরান্তের জেলাগুলোতে মানুষ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে কত কষ্ট করে যাতায়াত করতো!
স্বাধীনতার আগে বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকে তিস্তামুখ/ফুলছড়ি ঘাটে যে দুটো ফেরি চলাচল করতো, সেগুলোর নাম ছিল “এমভি শের আফগান” এবং “এমভি খালেদ”। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমনে দু’টি ফেরিরই সলিল সমাধি হয়। ১৯৭২ সালে ট্রেনে বাড়ি যাওয়া আসার পথে আমি একটা ফেরিকে যমুনার বালুচরে বালুর মধ্যে আটকা পড়া অবস্থায় দেখেছি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রেলওয়ে বাহাদুরাবাদ ঘাট - তিস্তামুখঘাটের মধ্যে যাত্রী পারাপারের জন্য দুইটা নতুন ফেরি চালু করে। তাদের একটার নাম ছিল “এমভি শেরে বাংলা” ও আরেকটির নাম “এমভি সোনারগাঁ”। এক শীতের দিনে ‘দিনের ট্রেনে’ অর্থাৎ “দ্রতযান এক্সপ্রেস” ট্রেনে বাড়ি যাবার সময় ঐ দুটো স্টীমারের একটিতে করে নদী পার হচ্ছিলাম। স্টীমারটি নদীর প্রায় তীর ঘেঁষে চলছিল কারণ ঐ জায়গাটাতেই জলের গভীরতা সবচেয়ে বেশি ছিল। আমি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পাড়ের দৃশ্য দেখছিলাম। একজন বয়স্ক ব্যক্তি হাট-বাজার করে ব্যাগ হাতে নিবিষ্ট মনে ধুলি ধূসরিত পাড় ধরে জুতো পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তার পাশ দিয়ে গুণ টেনে চলছিল একটি মাল বোঝাই নৌকোর মাঝিরা। উস্কোখুস্কো চুলের সেই বয়স্ক ব্যক্তিকে দেখে আমার কাছে দরিদ্র, কিন্তু অভিজাত ঘরের বলে মনে হয়েছিল। তখন সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। দূর দূরান্ত থেকে পাখিরা পাখা মেলে উড়ে এসে নদীতীরের গাছগাছালির উপর তাদের নীড়ের সন্ধান করছিল। আমার তরুণ মনে তখনকার দিনের খুবই জনপ্রিয় একটি গানের সুর বেজে চলেছিলঃ “নিঝুম সন্ধায়, পান্থ পাখিরা বুঝি বা পথ ভুলে যায়…..”!
১৯৮০ সালের প্রারম্ভে তৎকালীন রেলমন্ত্রী এবং জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ জনাব মশিউর রহমান যাদু মিঞা "একতা এক্সপ্রেস" নামে আরেকটি দ্রুতগামী ট্রেন উত্তরবঙ্গবাসীদের সুবিধার্থে চালু করেন। তখনকার দিনগুলোতে চলন্ত ট্রেনে একতারা-দোতারা বাজিয়ে বাউল ফকিরদের পরিবেশিত গান, অন্ধ ভিক্ষুকদের সুললিত কণ্ঠে পবিত্র ক্বোরআনের সুরা-আয়াত পাঠের মাধ্যমে অতি বিনয়ের সাথে ভিক্ষা মার্জনা, কথার যাদুতে যাত্রীদের মোহিত করে ধূর্ত কিন্তু পারদর্শী ক্যানভাসার কর্তৃক কৌশলে তার পণ্যসামগ্রী বিক্রয়, ইত্যাদি ছিল আমার অত্যন্ত নিবিড় মনযোগের বিষয়। ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামে কর্তব্যরত থাকাকালে আমাকে কয়েক মাসের জন্য সিলেটে ঘনঘন আসা-যাওয়া করতে হতো। তখন আমি "পাহাড়িকা এক্সপ্রেস" এ সিলেট যেতাম। সেটা ছিল রেলের যাত্রাপথে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শোভা সমৃদ্ধ রুট। বিশেষ করে ভানুগাছ ফরেস্ট এলাকায় কিংবা শ্রীমঙ্গলের লাউয়াছড়া এলাকায় যদি কোন কারণে ট্রেনটি ক্ষণিকের জন্যও থেমে যেত, তখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দু’চোখ ভরে নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করতাম। ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের পাশে ফুটে থাকা লজ্জাবতী গাছের লাজরাঙা ফুলগুলো দেখে শৈশবের কথা মনে পড়তো, যখন আমি লজ্জাবতী গাছ দেখলেই তার কোমল পাতাগুলো স্পর্শ করে ওদের বুঁজে যাওয়া দেখতাম। ঝোপঝাড়ের পাতায় পাতায় মনের সুখে ওড়াউড়ি করা বর্ণিল প্রজাপতি ও ফড়িং দেখে প্রফুল্ল হয়ে উঠতাম। ঐ সময়টাতে রেলে চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটেও বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছি। সেটাও রেলভ্রমণের জন্য চমৎকার একটি রুট ছিল।
ঢাকা
২৭ অগাস্ট ২০২৫
শব্দ সংখ্যাঃ ১০৮৫
(আমার এ পোস্টের ভাবনা ও স্মৃতিগুলো মনে উদিত হয়েছিল সম্প্রতি ব্লগার মঞ্জুর চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত "রেল যাত্রা" নামে একটি পোস্ট পড়ে।)

আদিতমারি রেল স্টেশন থেকে এ লাইনটা সোজা পশ্চিমদিকে চলে গিয়েছে "কাকিনা" রেলস্টেশনের দিকে। পূর্বপ্রান্তে ১০ কি.মি দূরে রয়ে গেল লালমনিরহাট রেলওয়ে জংশন।

স্বাধীনতার পর থেকে এই নতুন স্টীমারটিতে করে আমরা যমুনা নদী পার হ'তাম। ছবি স্বত্বঃ প্রকৌশলী নূরুস সাফা ভাই।
সর্বশেষ এডিট : ০৮ ই ডিসেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২:১৮


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।