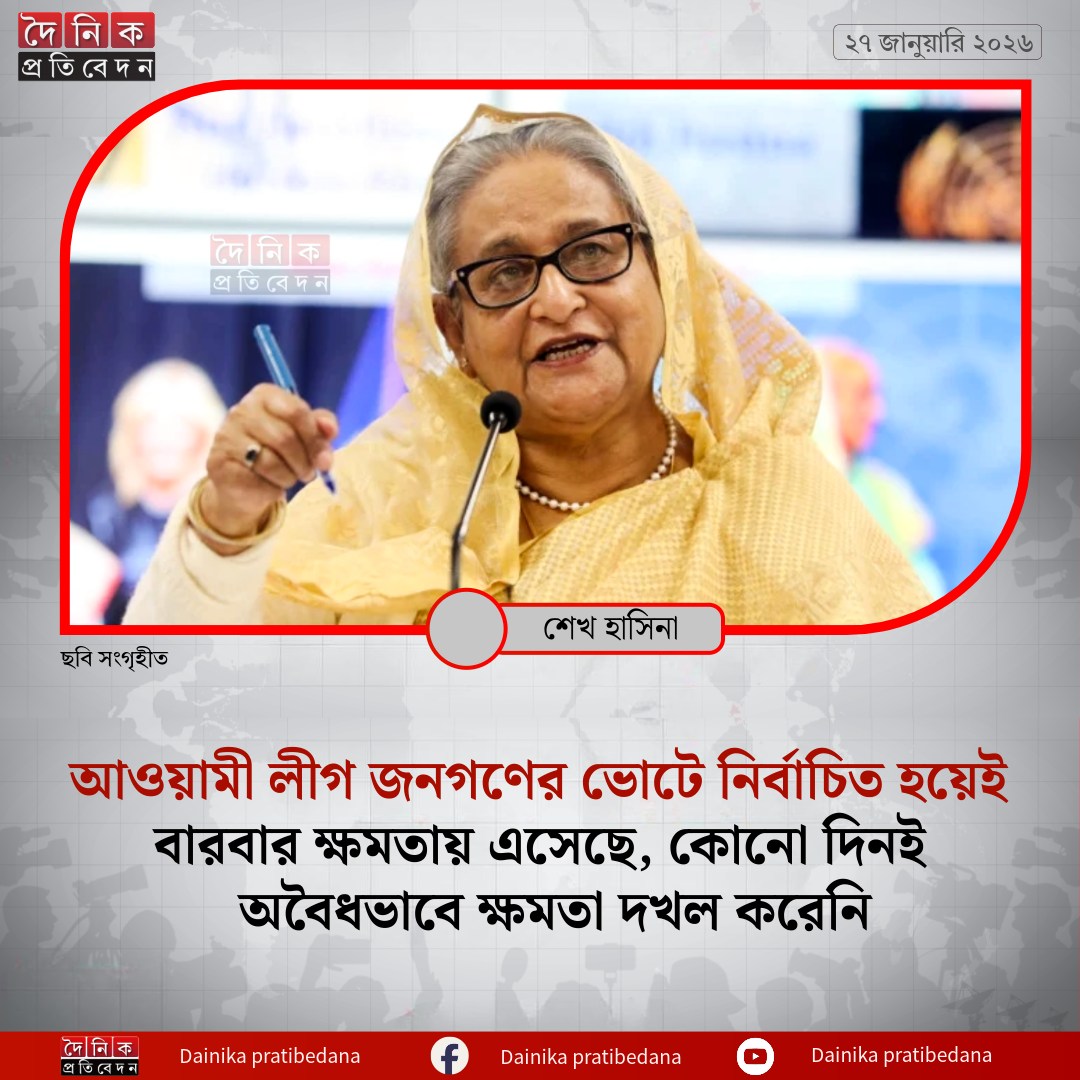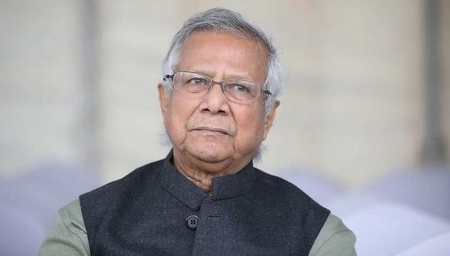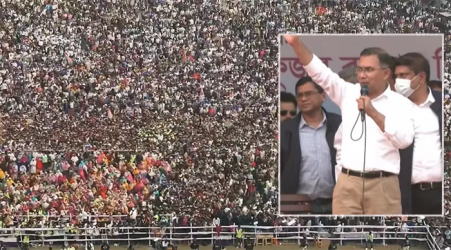১৯৪৩ সাল, চলছে মানব সভ্যতার ইতিহাসের ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। টোকিও শহর নিস্তব্ধ। যে কোন সময়ে বিমান আক্রমনের সাইরেন, বোমা হামলা। তার মাঝে মাথায় হেলমেট সহ এক বাঙালী নারী চলেছেন সেখানকার রেডিও ষ্টেশনের দিকে। বেতারের তরংগে ছড়িয়ে দিতে তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবান্বিত বিজয় গাঁথা, ইতিহাস হয়ে উঠবার আকাঙ্ক্ষা।
বলছিলাম বাংলার প্রথম নারী যিনি একজন ভিনদেশি বিয়ে করেছিলেন, বই লিখেছিলেন, জাপান গিয়েছিলেন, সেই হরিপ্রভা তাকেদার কথা। বর্তমান সময়ে আগামীর দিকে তাকিয়ে ইতিহাসে নথিতে যে অনুপ্ররণা খুঁজতে যাই। সেখানে নিজের প্রভায় নামের প্রভা ছড়ান হরিপ্রভা বসু মল্লিক। যদিও এই মহিয়ষী কে নিয়ে খুব বেশি প্রচার নেই।তাই হয়ত ২০২১ সালে হরিপ্রভা কে নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্রের নাম ‘অ্যান আনসাং ট্রাভেলার অফ বেঙ্গল’।
আধুনিক, সাবলম্বী নারী হরিপ্রভার জন্ম ১৮৯০ সালে। ঢাকা জেলার খিলগাওঁ গ্রামে। বাবা শশীভূষণ মল্লিক ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সক্রিয় কর্মী।১৮৯২ সালে তিনি ঢাকায় নিরাশ্রয় মহিলা ও শিশুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে মাতৃনিকেতন নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। যতটুকু জানা যায় শৈশব থেকেই হরিপ্রভা আশ্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন, ইডেন স্কুলে মেট্রিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ব্রাক্ষ্মসমাজের মেয়ে হিসেবে সুশিক্ষা, অপার স্বাধীনতা, সাথে পেয়েছিলেন মুক্ত চিন্তা করার দুর্দান্ত চিন্তাশক্তি।
আশ্রমে কাজ করার সুবাদে তার পরিচয় হয় জাপানি যুবক ওয়েমন তাকেদার সঙ্গে। তাকেদা তখন ঢাকায় কেমিস্ট হিসেবে কাজ করতেন। পরিচয়, আশ্রমের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, হৃদ্যতা এবং প্রণয়। ১৯০৭ সালে ১৭ বছর বয়সে পরিবারের সম্মতিতে নববিধান ব্রাহ্মসমাজে তাদের বিয়ে। বিয়ের পর ওয়েমন তার শ্বশুরে' র সহযোগিতায় ঢাকা সোপ ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেন। বছর খানেক পরে আর্থিক ক্ষতির মুখে, পাট চুকিয়ে সস্ত্রীক জাপানে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। ২২ বছর বয়সে সেই হরিপ্রভার প্রথম জাপান ভ্রমণ। সে যাত্রার সংবাদ প্রচারিত হতেই দেশে হইচই পড়ে যায়। দিনাজপুরের মহারাজা তাকেদা দম্পতিকে ২৫ টাকা এবং ঢাকায় বসবাসকারী জাপানি ব্যবসায়ী কোহারা তাদের ৫০ টাকা উপহার দেন। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে তাদের শুভকামনা প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। ৩ নভেম্বর ১৯১২ হরিপ্রভা ঢাকা থেকে প্রথমে নারায়ণগঞ্জ, সেখান থেকে স্টীমারে গোয়ালন্দ পরে ট্রেনে কলকাতা। ৫ নভেম্বর তারা কলকাতা থেকে জাহাজে করে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পোর্ট মোজিতে পৌঁছন ১৩ ডিসেম্বর। হরিপ্রভার জাপানে আগমন সংবাদ জাপানের দু'টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সফরে চার মাস সময়ে তিনি শুধু তার শ্বশুরবাড়িই নয় জাপানের সমাজ ব্যবস্থাকেও খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। তিনি জাপানের সামাজিক রীতিনীতির খুঁটিনাটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন। ১২ এপ্রিল ১৯১৩ তারা দেশে ফেরার যাত্রা শুরু করেন, ফিরে তিনি 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা' নামে একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন। যা সেসময়ে শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তোলে। যে জাপান সম্পর্কে তখনকার দিনে বাঙালির তেমন কোনো ধারণাই ছিল না, সেখানে পূর্ববঙ্গের এক নারী পৌঁছে গেলে এবং নিজের চোখ দিয়ে দেখা এক নতুন সমাজ-সংস্কৃতিকে সাবলীল ভাষায় বইয়ের পাতায় উঠিয়ে আনলে, সে বইয়ের একটি আলাদা কদর তো থাকবেই।
বই পড়ে আমরা জানতে পারি হরিপ্রভার জাপান দেখার আগ্রহ ছিল অপার। হরিপ্রভার নিজের লেখায় সেটা ফুটে উঠেছে -
“আমার যখন বিবাহ হয়, তখন কেহ মনে করে নাই যে আমি জাপান যাইব। কাহারও ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু আমার বড়ই ইচ্ছা হইত আমি একবার যাই। সে ইচ্ছা স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হইত। বিবাহের পর শ্বশুর-শ্বাশুড়ির আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে ইচ্ছা হইত। তাঁহাদের নিকট পত্র লিখিয়া যখন তাহাদের ফটোসহ আশীর্ব্বাদ পূর্ণ একখানি পত্র পাইলাম ও তাঁহারা আমাদের দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পত্র লিখিলেন, আমার প্রাণ তখন আনন্দে ভরিয়া গেল। তাঁহাদিগকে ও তাঁদের দেশ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে চলিল।
জাপানে গমন, আতিথেয়তা, ভারতীয়দের নিয়ে জাপানিদের ঔৎসুক্য, সে সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উঠে আসে লেখায়। শহর কোবে, টোকিও, ওসাকা ভ্রমণের কথা ও শ্বশুরবাড়ির গ্রামে যাওয়ার বর্ণনা আছে এ গ্রন্থে। ছোট পরিসরে হলেও তিনি জাপানী সমাজ, রাস্তাঘাট, ধর্ম, কৃষি, বাড়িঘর, পোশাক, খাদ্য ও জাপানীদের চালচলনের কথা লিখেছেন। ১৯১৫ সালে উয়ারীতে মুদ্রিত বইয়ের মূল্য রাখা হয়েছিল চার আনা।
রবি ঠাকুরের ‘জাপান যাত্রী’- বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। নিঃসন্দেহে সে লেখায় জাপানি নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু সেই বই এর প্রায় দশ বছর আগে এক বাঙালি নারীর ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি এবং জীবনদর্শনও খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধরা দেয়, হরিপ্রভার লেখায়। হরিপ্রভার যে যে প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিলো তার প্রমাণ আমরা উনার লেখায় পাই, ভ্রমণ কালে উনি নিজস্ব সেই প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি কে কাজে লাগিয়ে জাপানের সামাজিক রীতিনীতি ও আদবকায়দাগুলো খেয়াল করেন, এবং বাংলায় দেখে যাওয়া সমাজের রীতি ও প্রথার সাথে তুলনা করে লিপিবদ্ধ করেন পাতায়।
“মেয়েদের পতি, বাড়ির আত্মীয়-স্বজন ও শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা পরম ধর্ম। ইহার কোনোরূপ অন্যথা হইলে স্ত্রী অত্যন্ত লাঞ্ছিত হন। এমনকি শাশুড়ির অপছন্দ হইলে স্বামী অনায়াসে স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারেন।”
জাপানের মন্দির, নববর্ষের উৎসব, মেয়েদের স্কুল, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিকতা, আচার-অনুষ্ঠান, গৃহস্থালির খুঁটিনাটি ইত্যাদি নানা বিষয়ের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। তিনি দেখেছিলেন, জাপানে মেয়েরা ভারতবর্ষের মতো পর্দানশিন বা গৃহসীমায় আবদ্ধ নয়। “বাজারে, দোকানে, স্টেশনে, পোস্টাফিসে সর্বত্র মেয়েরা কাজ করে। আমোদ প্রমোদ স্থলে যেখানে অত্যন্ত জনতা হয়, মেয়েরা সেখানে তত্ত্বাবধান করে। তামাশা দেখার জন্য টিকিট বিক্রয়াদি মেয়েরাই করে। মেয়েদের অবরোধ নাই; তাহারা পুরুষের সঙ্গে একত্রে কাজকর্ম করে, চলে ফেরে, তাহাতে কোন বাধা বা সঙ্কোচ নাই।”
শুরুতে লিখেছি এক অকুতভয় রমণীর জীবন যুদ্ধের স্মৃতি, যা হরিপ্রভার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাপান সরকার সমস্ত জাপানি নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে নেয়। ১৯৪১ সালে স্বামীর সাথে পাকাপাকি ভাবে জাপানে থাকার উদ্দেশ্যে বোম্বে থেকে জাহাজে উঠতে হয় হরিপ্রভাকে। জাপানে গিয়ে প্রথমবার যে আত্মীয়স্বজনদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, এবার কোনোকিছুই ছিল না। একসময়কার শান্ত-সুশৃঙ্খল জাপান যুদ্ধের তাণ্ডবে পুরোপুরি বিপর্যস্ত। চলছে অর্থনৈতিক সঙ্কটও। ফলে হরিপ্রভাদের বাসস্থান বা উপার্জন কিছুই ছিল না। সাথে স্বামী উয়েমনের শারীরিক অসুস্থতা, সব মিলিয়ে সমস্যা ক্রমশ প্রকট হতে থাকে হরিপ্রভার জন্য। গভীর রাতে মাথায় হেলমেট দিয়ে চলে যেতেন টোকিও রেডিও স্টেশনে। শুরুর দিকে পরনে শাড়িই থাকত। কিন্তু ঠিকমতো যে বাড়িতে ফিরতে পারবেন, তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই পেটিকোটে একটি পকেট বানিয়ে সেটির ভেতর পাসপোর্ট, টাকাপয়সা, গয়নাগাটি বহন করতেন তিনি। যুদ্ধ শেষ হবার আগে দিনদিন পরিস্হিতি আরও খারাপ হতে শুরু করলো। ক্রমেই রেল লাইন ধ্বংস , রেকর্ড প্রস্তুত কারখানা ধ্বংস। হিন্দি ফৌজের রেকর্ডিং ও বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ জাপানের সাধারণ জীবনে যে ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছিল, সেই আতংক লিখেছেন তিনি। ডিসেম্বরের এক বিকেলের বিবরণ দিয়েছেন হরিপ্রভা এভাবে -
“বিকেল সাড়ে তিনটায় রেইড বন্ধ হওয়া মাত্র বেড়িয়ে পড়ি , রেইড এরপর একা পথ চলা আমার পক্ষে দুষ্কর বিধায় আমি ঐ বাড়ির ১৩ বৎসর বয়স্কা মেয়েটিকে নিয়ে রওনা হই। রেললাইন নষ্ট হওয়ায় গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েটি আমায় তাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিতে চায়। আমাদের বাড়ি ও স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় আমার বাড়ি যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। … ট্রেন পথ ছেড়ে অন্য রাস্তার লাইনে দাঁড়িয়ে ট্রামে অতিকষ্টে উঠে যতটা সম্ভব এগিয়ে অতঃপর মধ্য পথ থেকে হেঁটে বাড়ি চললাম। রাস্তার দুপাশে বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, জল কাদা ছাই ইলেকট্রিক তার ছড়াছড়ি। আমাদের বাড়ির এলাকায় এই কাণ্ড দেখে আমি ত মৃতপ্রায় হয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে পথ চলছি। গাড়ি বোঝাই মড়া, ট্রেচারে আহতদের নিয়ে চলেছে। ভগবানকে ডাকতে ডাকতে রাত্রি ১০ টায় বাড়ির দিকে কিছুটা যেয়ে দেখি, এই পাড়া বেঁচে গ্যাছে।’’
১৯৪৫ এর অভিশপ্ত ৬ আর ৯ আগস্ট জাপানেই ছিলেন। হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে আণবিক বোমা পতনের অভাবনীয় ধ্বংসলীলা নিয়ে বেশি কিছু লেখা নেই।

ছবিতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে হরিপ্রভা তাকেদা।
১৯৪৭ সাল যুদ্ধ শেষ, শুরু হয় এই অভিযাত্রিক রমণীয় জীবনের তৃতীয় ও শেষ অধ্যায়। অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে দেশে ফিরে পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়িতে বোন অশ্রুবালা মল্লিকের সাথে বসবাস শুরু। পরের বছর স্বামী অনন্তে পারি জমান। স্বামীর মৃত্যুর পরও ভেঙে পড়েননি, থেকেছেন দৃঢ়চেতা এবং সমাজ কর্মী। একাকী জীবনে একবার ভয়ংকর দুষ্কৃতিকারীর হামলায় ভীষণ ভাবে আহত হন, সে সময়ে হাসপাতালে ভর্তি! তখন ও প্রিয়জন দের সাহস যুগিয়েছেন
" ওরে তোরা ভয় পাস নে, আমার কিছু হবে না আমি যে মেইড ইন জাপান !
হরিপ্রভা তাকেদা' র পরিচয় তার লেখায়, একটা ছোট্ট বই যে কত সাধারণ অথচ আকর্ষণীয় হয় ! কতভাবনার জন্ম দেয়! কত উত্তর না জানা প্রশ্ন মনে ভিড় করে! এই বইটি না পড়লে বুঝা মুশকিল। সব সময় কি সবাই একটা উন্নত সাহিত্য মান সম্পন্ন বই খুঁজি? ভালো লেখা কি সব সময় মনে আনন্দ দেয় ? সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণেও কিছু লেখা আকর্ষণীয়। তার লেখা " বঙ্গ মহিলার জাপান যাত্রা" টি বাংলায় লেখা সেরা ১০০ ভ্রমণ বই এর তালিকায় স্থান পেয়েছে। রচিত অনান্য গ্রন্থাবলী জ্ঞানদেবী, আশানন্দ ও ব্রহ্মনন্দ কেশবচন্দ্র সেন। এছাড়া সমসাময়িক পত্রিকায় জাপানী জীবন যাত্রা নিয়ে ধারাবাহিক ও লিখেছেন তিনি।
১৯৭২ সালে এই অভিযাত্রি তার শেষ ভ্রমন যাত্রা শুরু করেন, অনন্ত মহাকালের যাত্রা।
তথ্যসূত্রঃ উইকি পিডিয়া।
প্রথম আলো

সর্বশেষ এডিট : ২৪ শে মে, ২০২৪ সকাল ১১:৪০


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।