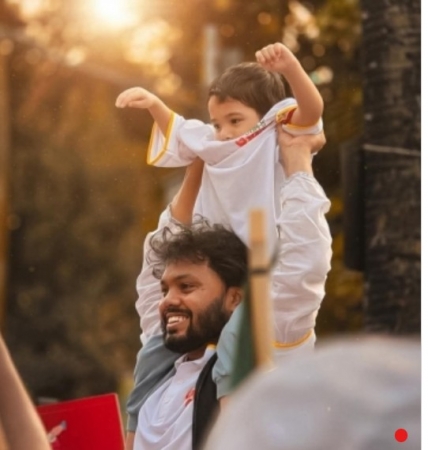মানুষের মুক্তি-চতুর্বর্গ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা
প্রসিদ্ধ ফরাসী মাজ-দার্শনিক রুসো লিখেছিলেন-মানুষ জন্মায় মুক্ত অবস্থায় কিন্তু জীবন কাটায় শৃঙ্খলিত হয়ে, দাস অবস্থায়। মানুষ যতদিন থেকে তার অবস্থা নিয়ে চিন্তা করে আসছে ততদিনই তার চিন্তায় মুক্তি কোন্ পথে অর্জন করা যায় সে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এই চিন্তা দুই খাতে প্রবাহিত হয়েছে। একটি খাত ধর্মীয় চিন্তার। অপরটি সমাজচিন্তার। ধর্মীয় চিন্তার খাতে প্রবাহিত মুক্তির অনুসন্ধান ঘুরে-ফিরে একই উত্তরের মোহনায় উপনীত হয়েছে-জীবদ্দশায় মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। অধিকাংশ সাধারণ স্তরের ধর্মচিন্তায় এই মুক্তির আশ্বাসকে দেওয়া হয়েছে পুণ্যের ফল স্বরুপ পরলোকগত আত্মার স্বর্গলাভ। আমাদের দেশের অধিকতর জটিল ধর্মচিন্তায় মুক্তিকে বোঝা হয়েছে মোক্ষ বা নির্বাণের অর্থে। স্বর্গপ্রাপ্তি বা পূনর্জন্ম, উভয়ক্ষেত্রেই আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান। এই অস্তিত্ব যতক্ষন রয়েছে ততক্ষণ আত্মার মুক্তি নেই। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াই আত্মার একমাত্র মুক্তি। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই সামাধানটি হচ্ছে মাথাব্যথার দাওয়াই হিসাবে মাথাটাকেই কেটে বাদ দেওয়া। আমরা এই ধর্মীয় মুক্তির ধারনাতে আগ্রহী নই। মানব জীবনকে চূড়ান্ত মূল্য দিয়ে জীবিত অবস্থাতেই মুক্তি কিভাবে পাওয়া যেতে পারে সেই প্রশ্নটাই আমাদের আলোচ্যবস্তু।
মানুষকে দাসাবস্থায় আবদ্ধ রেখেছে চার রকমের শৃঙ্খল। চার রকম বিরোধী-শক্তির অধীন হয়ে মানুষকে জীবন-যাপন করতে হয়। প্রথমটি হলো, প্রাকৃতিক শক্তি। ইতিহাসের আদিযুগে প্রাকৃতিক শক্তিদের তুলনায় মানুষের শক্তি ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রাকৃতিক অবস্থায় সামান্য হেরফের হলেই মানুষ তার জীবনরক্ষার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হিংস্র জন্তু এবং সর্বোপরি বিভিন্ন ব্যাধির সম্মিলিত ফল হিসাবে সেই সময়ে মানুষের মৃত্যুর হার ছিল অত্যন্ত বেশি, গড় আয়ু ছিল অত্যন্ত কম। প্রকৃতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে মানুষের চিন্তা দু-টি পথ অবলম্বন করেছিল। এক হলো প্রকৃতিক শক্তিদের মধ্যে দেবতা, দানব ও অন্যান্য মূলত হিংস্র, যুক্তিহীন খামখেয়ালী মনবিশিষ্ট সত্তাদের অস্তিত্ব আরোপ করে নেওয়া এবং তাদের সঙ্গে সহবাস করার তণ্ত্রমণ্ত্র-তুকতাক-যাদু প্রভৃতির উপায়ের উদ্ভাবন করা। দ্বিতীয় হলো-বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথ। যুক্তির উপর ভিত্তি করে নেওয়া এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রাকৃতিক শক্তিদের মধ্যে মানুষ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে এক অমোঘ নিয়মের রাজত্ব। একবার নিয়মগুলিকে বুঝে উঠতে পরার পর মানুষ সমর্থ হয়েছে নিত্যনতুন উপায়ে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে ইচ্ছামতো চালিত করতে। এখনো অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মগুলোকে জানার বাকি আছে-সেই জানার কাজ কোনদিনই সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভরতা যে কতদূর কমে গিয়েছে তা যে কোন সাধারণ মানুষেরই জানা। উদাহরণ হিসাবে বৈজ্ঞানিক চিকিতসাবিদ্যার কথা যদি ধরা যায় তো দেখা যায় যে, এক কর্কটরোগ আর হৃদরোগ বাদ দিয়ে এমন কোন রোগই বাকি নেই যার প্রতিষেধক না আবিষ্কৃত হয়েছে, যদি প্রায়োগিত পদার্থবিদ্যার কথা ভাব তো পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, চন্দ্র গ্রহে মানুষের পদার্পণ ও প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি এক বিশাল তুলনাহীন অগ্রগতির নাটকীয় নিদর্শন মাত্র।
আমাদের দেশে এখনো অবশ্য অনেক লোকই আছে (সংখ্যায় তারাই গরিষ্ঠ) যারা এখনো মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, কোষ্ঠী, হস্তরেখা প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে। কিন্তু এরাও না মেনেই পারবে না যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতিকে চোখে দেখা যায়; প্রতিনিয়ত, প্রতিদিনিই অগ্রগতি ঘটছে। আজ যাসম্ভব নয় কাল তা সম্ভব হচ্ছে। মন্ত্রতন্ত্র-তুকতাকের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগে যা সম্ভব ছিল আজ তার চেয়ে অধিক কিছু সম্ভব বলে কুসংস্কাচ্ছন্ন ব্যক্তিদেরো কেউ দাবি করে না।
দ্বিতীয় যে শৃঙ্খলের দ্বারা মানুষ আবদ্ধ তা হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাজনিত। ইতিহাসের আদিযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যখন সংঘবদ্ধভাবে বাস করেছে তখনই সেই সংঘ আকার নিয়েছে কোন না কোন সমাজব্যবস্থার, যে ব্যবস্থার মূলে আছে কোন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং যাকে ধারণ করে রেখেছে বিশেষ গঠন সমন্বিত কোন এক রাষ্ট্র। ইতিহাসের যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সমাজে এক অংশের ব্যক্তিদের দ্বারা উতপাদনের কার্য করিয়ে নিয়ে সেই উতপাদনের উদ্বৃত্তের অংশ দিয়ে বাকি অংশের জীবিকা নির্বাহ তথা বিলাসবহুল জীবনযাপন সম্ভব করা। এই শোষণ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো উতপাদিকা শক্তিদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা। প্রকৃতিদত্ত সম্পদ, যেমন কৃষিযোগ্য জমি, খনিজদ্রব্য এবং পরবর্তীযুগে উতপাদনের যন্ত্রপাতির উপর মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির মালিকানার ভিত্তিতে সমাজে সৃষ্ট হয় আর্থিক বন্টন-বৈষম্য। ঐতিহাসিক যে কোন পর্বে অনুন্নত উতপাদন তথা বন্টন-বৈষম্যের দরুন অধিকাংশ মানুষেরই ভাগ্যে যে পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য জুটেছে তা অকিঞ্চিতকর; তার দ্বারা যে জীবনমান সম্ভব হয়েছে তা জন্ত-জানোয়ারের জীবনমানের চেয়ে সামান্যই ঊর্ধ্বে। শোষক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সেই সম্প্রদায়ের অনুগ্রহভাজন মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি মাত্র সুযোগ পেয়েছে ঊর্ধ্বস্তরের জীবনযাত্রার। যারা বিলাসী জীবন-যাপন করেছে শুধু তারাই এই মুষ্ঠিমেয়র অন্তর্ভুক্ত নয়, বিজ্ঞান-কলা-সাহিত্য প্রভৃতির চর্চা করে যারা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেল তরাও এই শোষণজাত উদ্বৃত্তের অংশ ভোগ করেই তা করতে সমর্থ হয়েছে। অর্থনৈতিক অভাবের দুরণ অধিকাংশ মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হওয়াকেই আমরা মানুষের দ্বিতীয় শৃঙ্খল বা দ্বিতীয় দাসত্ব বলে অভিহিত করেছি।
তৃতীয় শৃঙ্খলটি হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিনিষেধজনতি। উতপাদন, শোষণ ও বন্ট-বৈষম্যের ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে প্রয়োজন হয় এক সামাজিক কাঠামোর। সেই কাঠামোকে ধারণ করে রাখার জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র মানেই আইন এবং সেই আইনের সার্থক প্রয়োগের জন্য দন্ডদানের ক্ষমতা। রাষ্ট্র ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। ব্যক্তি যা করতে চায় তার সবকিছু সে করতে পারে না আর্থিক সামর্থ্য থাকলেও-আইনের বাধার দরুন। আইন ছাড়াও অনেক বিধিনিষেধ আছে যাদের প্রয়োগ করা হয় সামাজিক চাপের মারফত। সমাজসম্মত কাজ না করলে ব্যক্তির সমাজে একঘরে করে রাখা হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের গন্ডিতে আবদ্ধ থাকাকেই আমরা বলছি মানুষের তৃতীয় পর্যায়ের দসত্ব।
চতুর্থ পর্যায়ের শৃঙ্খলটা হচ্ছে আমাদের নিজেদেরই মনের সেই অংশ যা ভরা রয়েছে নানাবিধ কুসংস্কার ও মানবতাবিরোধী ভাবধারায়। সামাজিক জীবনে প্রতিনিয়ত আমরা নিজেদের নানাভাবে ক্লেশ দিচ্ছি এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিদের ক্লেশ দিচ্ছি এই ভাবনগুলির দ্বারা চালিত হয়ে। আমাদের অনেক প্রবৃত্তিকে আমরা দমন করছি, আমাদের অনেক সম্ভাবনাকে বাস্তব হয়ে উঠতে দিচ্ছি না এইসব জীবনবিরোধী ধারণাগুলির কারণে। কয়েকটা উদাহরণ নেওয়া যাক। পণপ্রথার কুফল নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। বহুদিন আগে থেকেই সকলে মেনে নিয়েছে যে প্রথাটা অত্যন্ত খারাপ। তা সত্ত্বে ও প্রথাটা অবলুপ্ত হচ্ছে না। রাষ্ট্র জোর করছে না। পণ না নিলে সমাজে কাউকে একঘরে করা হয় না; আর্থিক প্রয়োজনে পাত্রপক্ষ পণ নিতে বাধ্য হয় তাও ঠিক নয়, কারণ যে পাত্রপক্ষ যতবেশি ধনী তাদের পণের দাবিও হয়ে থাকে সেই তুলনায় উচ্চগ্রামের। প্রথাটা যে থেকেই যাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ কন্যাপক্ষেরই পণের পরিমাণের সঙ্গে নিজেদের পারিবারিক মর্যাদাকে এক করে দেখার প্রবণতা। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবেই শাশুড়ি-ননদ প্রভৃতিদের হাতে নববধূরা যেভাবে নিগৃহীত হয় তার কথাও কারোও অজনা নয়। এই অত্যাচারের পিছনেও না আছে কোন শ্রেণী-সংগ্রামের ভূমিকা না আছে অত্যাচারী রাষ্ট্রের শাসন। বৌয়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে শাশুড়িকে একঘরে করা হয় না; তা সত্ত্বেও বৌদের ওপর অত্যাচার হয়েই চলেছে। অত্যাচারকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বৌকে খুন করে মারা হচ্ছে অথবা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বৌ আত্মহত্যা করছে-এই জাতীয় ঘটনা কম হওয়ার কোনই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শুধু বৌ নয়, বাড়ির মেয়েরাও ছেলেদের থেকে অনেকভাবে অবহেলিত হয়ে থাকে। সমাজে পদে পদে নারীদের নারী হওয়ার অপরাধে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়। প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে, শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও ধরেই নিয়েছে যে স্ত্রীজাতির চেয়ে পুরষজাতি উন্নতস্তরের জীব; তাদের বুদ্ধি বেশি, ক্ষমতা বেশি, প্রতিভা বেশি, ন্যায্যতই তাদের নারীদের চেয়ে অধিক সুখ-সুবিধা প্রাপ্য; পুরুষের সেবাই নারী-জীবনের লক্ষ্য ও সার্থকতা। জাতিভেদের বিষয়টাও এই পর্যায়ে পড়ে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই ভেদব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য ক্রুর সামাজিক শক্তির ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। বরং রাষ্ট্র থেকেই তথাকথিত নিচু জাতির লোকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতিপ্রথার গুরুত্ব খুব কমে নি। বাঙালী সমাজে ব্রাক্ষণ-কায়স্থ-বদ্যিদের মধ্যে এখনো জাত্যাভিমান অত্যন্ত প্রবল। নিচুজাতের মেয়ে বিয়ে করলে কোন ছেলেকে জেলে দেওয়া হয় না, চাকরিতে বা শহরাঞ্চলের পাড়ার সমাজেও কোন অসুবিধা হয় না, তা সত্ত্বেও ভিন্নজাতের মধ্যে বিবাহ সংখ্যা এখনো নগণ্য। এই প্রথার দরুন যে পাত্রপাত্রী নির্বাচনের গন্ডিটা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায় তার পিছনে নিজেদের মনের বাইরের কোন বৈরী শক্তিকেই সনাক্ত করা যায় না।
(চলবে)
(লেখাটি উৎস মানুষ সংকলন এর “শেকল ভাঙা সঙস্কৃতি” বই থেকে নেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পুরো বই-টি তুলে ধরব। কারণ, এ বইটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের সবার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি বই বলে আমি মনে করি।)
সর্বশেষ এডিট : ১৫ ই ডিসেম্বর, ২০০৯ বিকাল ৪:২৩


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।