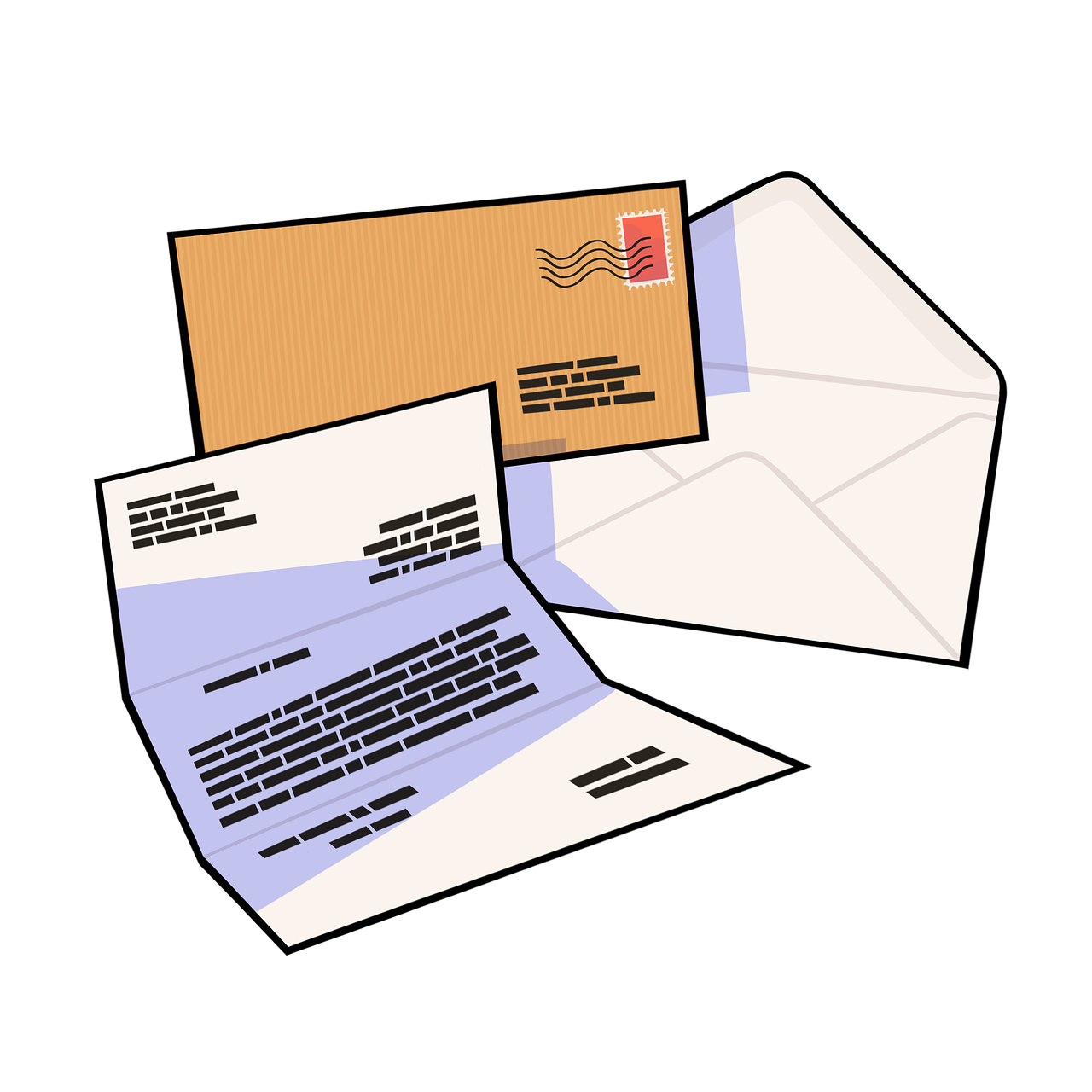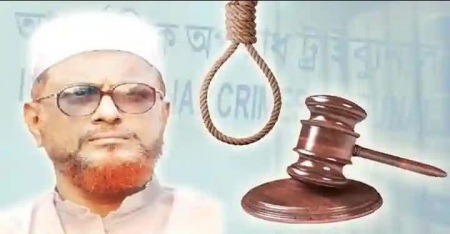১ম পর্ব
শুয়োর
মৌসুমী গেস্ট হাউজেই নেত্রকোনার প্রথম শুয়োরটা দেখলাম। পেটে দড়ি দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। দিদি জানালেন – গারো বিয়ে উপলক্ষ্যে কেনা হয়েছে শুয়োরটি, দাম পড়েছে বিশ হাজার টাকা। দুই দিনে আরও বেশ কয়েকবার শুয়োর দেখেছি। পাহাড়ের দিকে গেলে গারো বাড়ি দেখা যায়। সেখানে বাড়ির সামনে শুয়োর বাঁধা দেখলাম কয়েক জায়গায়।
নেত্রকোনা থেকে ফিরে আসার জন্য যখন গেস্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে এসেছি তখন একটা বেশ বড়সড় শুয়োরকে ভ্যানের উপরে রেখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শুয়োরটা মৃত। আমি জিজ্ঞেস করলাম – মরে গেছে? ওরা বলল, মরে নাই, মেরে এনেছি। উত্তরে আমি একটু অবাক হলাম। কারণ শুয়োরের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, তাহলে মারলো কিভাবে?
উত্তর পেয়েছি সিএনজি চালকের কাছ থেকে। তিনি জানালেন, গারোরা শুয়োরের হৃদপিন্ড বরাবর লোহার শিক ঢুকিয়ে দেয়, তাতেই মরে যায় শুয়োর (সত্যতা নিয়ে সন্দেহ আছে)। মৃত শুয়োরকে ফুটন্ত পানিতে কিছু সময় ডুবিয়ে রাখলে চামড়ার পশমগুলো নরম হয়ে যায়। তখন টেনে টেনে ছিড়তে হয়। কালো শুয়োর তখন সাদা হয়ে যায়। তারপর মৃত শুয়োরটাকে আগুনে পোড়ানো হলে গায়ের রঙ হয় বাদামী। এবার শরীরের চামড়া ছড়িয়ে মাংস বের করে আনা হয়, কেটে টুকরো করা হয়। তারপর নানা রকম মশলা মিশিয়ে রান্না হয়।
গারোরা মাংসের জন্য শুয়োরের উপর নির্ভরশীল। এজন্য অনেকে ঘরেই শুয়োর পালে। উৎসবে শুয়োর খাওয়া হয়। মোরগও সাধারণত উৎসবের খাবার। আর উৎসব মানেই চু এর স্রোতস্বিনী। চু হলো এক ধরণের মদ যা সাধারণত চাল, গম, ভুট্টা আর এক ধরণের আলু (গারো আলু নামে পরিচিত) মিশিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই মদ তৈরি করা হয়। গারোদের যে কোন অনুষ্ঠানেও চু পান করা হয়। এটি তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আমাদের বাচ্চাদের জন্মের পরে মধু দেয়ার প্রচলন আছে, গারোরা মধুর পরিবর্তে চু-তে আঙ্গুল ডুবিয়ে শিশুর মুখে দেয়। এতে বোঝা যায়, চু তাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
আগেরবার গেস্ট হাউজেই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এখানে সেরকম ব্যবস্থা ছিল কিন্তু আমরা স্থানীয় হোটেলেই খেয়েছি। সুজন ভাই আগেই বলেছিল, খেতে গিয়ে উনার কথার সত্যতা টের পেলাম। শুটকী, গরু, কালাভুনা, কলিজা, ভর্তা, ডাল – কোন খাবারেই স্বাদ পাওয়া গেল না বরং অনাবশ্যক ও মাত্রাতিরিক্ত ঝালে মুখ পুড়ে গেলো। বাচ্চারা খেতে পারলো না। খাবার হোটেল হাতে গোনা, তার তিনটিতে চারবেলা খেয়েছি। একই রকম – আলমগীর হোসেন ভাই ভাই রেস্টুরেন্ট সামান্য ব্যতিক্রম হওয়ায় সেখানে দুই বেলা খাওয়া হলো। সকল তরকারির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো – ওগুলো বরফের মতো ঠান্ডা। সকাল-দুপুর-রাত যে সময়েই হোক না কেন। আমার কপাল ভালো – রাতে খিচুড়ি আর ডিম ভাজি খেয়েছি – দুটোই চুলার উপর থেকে এনে পরিবেশন করায় ঠান্ডা খেতে হয়নি।
চা এর কথা বলে নেই। কোন রেস্টুরেন্টেই চায়ের ব্যবস্থা নেই। তবে চাইলে এনে দেয়। ওয়াইডব্লিউসিএ-এর রাস্তায় প্রবেশের আগে বাম কোনায় একটা চায়ের দোকান আছে – গরুর দুধের চা পাওয়া গেল। অপেক্ষাকৃত ভালো। ওখানে মালাই বিক্রি হচ্ছিল – প্রতি কাপ পঞ্চাশ টাকা। রাতে খেতে এসে দেখি শেষ, সকালে গিয়ে দেখি তৈরি হয়নি। ফলে মালাই চেখে দেখার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হতে হলো।
সোমেশ্বরী নদী
সোমেশ্বরী নদী দেখবো বলে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ছিলাম – খাওয়ার পর তাই সেদিকেই রওয়ানা হলাম। দশ বছরে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। তখন মোটরসাইকেলের পেছনে বসে যেতে হতো। আমরা হেঁটে গিয়েছি-ফিরেছি। এখন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ছড়াছড়ি। বিরিশিরি কালচারাল একাডেমির সাথেই ময়মনসিংহ বাসস্ট্যান্ড, আর সেখান থেকেই অটো রিজার্ভ করে চীনামাটির পাহাড়ে যাওয়া যায়। বারোশ টাকা চাইল, ব্রিজের জন্য নাকি দুইশ টাকা দিতে হবে। ধূলোর রাজ্যে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবিয়ে আমরা হেঁটেই চললাম।
নদীর তীরে গিয়ে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। কোথায় সোমেশ্বরী নদী? কোথায় সেই চিকচিকে বালুময় তীর? কোথায় স্বচ্ছ স্ফটিক জল? কিচ্ছু নেই। যেদিকেই তাকাই কেবল ড্রেজার আর ট্রাক। প্রচন্ড শব্দে ড্রেজার চলছে, নদী থেকে বালু উঠছে ট্রাকে। সেই ট্রাক সারি বেঁধে উঠে যাচ্ছে সড়কে।
সবচেয়ে কষ্ট লাগলো নদীর অবস্থা দেখে। মাটি আর বালু ফেলে নদীর বুক চিড়ে রাস্তা বানানো হয়েছে। সেই রাস্তায় ধূলো উড়িয়ে যাচ্ছে ট্রাক। সেই রাস্তা ধরেই চলছে মানুষ, গরু-ছাগল। নদীতে প্রবাহমান কোন পানি নেই। জায়গায় জায়গায় আবদ্ধ পানি। বালু তুলে জমা করে রাখায় মরুভূমির মত দেখাচ্ছে। নদীর অপর প্রান্তে এক-দেড়শ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি কাঠের সেতু তৈরি করা হয়েছে, সেখানে কতগুলো লোক চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে আছে। হেঁটে পারাপারে জনপ্রতি পাঁচ টাকা করে নিচ্ছে। অটোরিকশা গেলে দুইশ টাকা।

এক দশক আগে যখন এসেছিলাম তখন ঠিক এই জায়গাটায় ছিল স্বপ্নের মতো চমৎকার এক নদী। নদীর পানি টলটলে স্বচ্ছ, ঠান্ডা, বয়ে যাচ্ছে কুলকুল করে। পা ডুবিয়ে দাঁড়ালে মন ভিজে যায়, শীতল হয়। নদীতে খেয়া ছিল। জনপ্রতি চার বা পাঁচ টাকায় নদী পার করে দেয়। আমরা অবশ্য হেঁটেই পার হয়েছিলাম, সর্বোচ্চ গভীরতা কোমড় পর্যন্ত। ফেরার সময় এই নদীতেই গা ডুবিয়ে শুয়ে ছিলাম, গোসল করেছি দীর্ঘ সময় নিয়ে। রাতে ফিরে এসেছি বালুময় সৈকতে, চাঁদের আলোয় নদীর পাড়ে হেঁটেছি, বসে থেকে জোৎস্না দেখেছি। সেই একই নদীর এই দুর্দশা সহ্য করা যায় না।

এই ছবিটা এক দশক আগে তোলা
অবশ্য নদীর এই কদাকার রূপ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি বিরিশিরিতে পৌঁছার সময়েই। রাস্তায় প্রায় শ’খানেক ট্রাক দেখেছি। বালু কেনা-বেচার হাট দেখেছি ডজনখানেক। রাস্তায় ধূলার পুরু স্তর আর ঢেউ খেলানো রাস্তা দেখে বুঝেছি ভারী সব ট্রাকের চলাচল হলো এর কারণ।
বালুখেকোরা সোমেশ্বরীকে কিভাবে ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে তা নিয়ে প্রথম আলো পত্রিকায় একটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল গেল বছরের জানুয়ারিতে। বাংলাদেশ সীমান্তের এক কিলোমিটার থেকে শুরু করে সাড়ে চার কিলোমিটার ভাটিতে অন্ততঃ পাঁচটি বালুমহাল ঘোষণা করা হয়েছে। লক্ষ থেকে থেকে শুরু করে কোটি টাকায় সেই বালুমহালের ইজারা নিয়েছেন এবং বছর বছর চুক্তি নবায়ন করছেন স্থানীয় সরকারদলীয় নেতারা। তারা জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা ও চুক্তি ভঙ্গ করে পরিবেশ দূষিত করে এবং শত শত ড্রেজার ব্যবহার করে দিনরাত নদী থেকে বালু তুলছে। সাথে উঠছে পাথর ও কয়লা। ড্রেজার ব্যবহারের কারণে নদীর ৫০-৮০ ফুট গভীর থেকে বালু-পাথর উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে। এভাবে দৈনিক উত্তোলিত বালুর পরিমাণ পাঁচ লাখ ঘনফুট।
নদীর অপর পাড়ে অনেকগুলো অটোরিকশা দাঁড়িয়ে ছিল। এখানেও সিন্ডিকেট। রিজার্ভ নিতে হলে সিরিয়ালের প্রথম অটোকেই ভাড়া নিতে হবে৷ ভাড়া দরকষাকষি করে দিচ্ছেন যিনি তিনি আবার অটোচালক নন। সেখান থেকে সাড়ে পাঁচশ টাকায় পাঁচটি স্পট ঘুরিয়ে আনার জন্য একটি অটো ভাড়া নেয়া হলো।
এই রাস্তা সোজা চলে গেছে বিজয়পুর বিজিবি ক্যাম্প পর্যন্ত। পিচঢালা রাস্তা। তবে এখানেও প্রচুর ধূলা। শীতকালে ধূলা উড়বেই। তার উপর এ অঞ্চলটা একটু রুক্ষ এবং পাশেই নদী থেকে বালু তোলা হচ্ছে। শান্তির ব্যাপার হলো – এই রাস্তায় বালুর ট্রাক চলছিল না।
(২য় পর্ব সমাপ্ত)
(প্রায় তিন হাজার শব্দের হওয়ায় মোট চারটি কিস্তিতে প্রকাশ করবো। একসাথে পড়তে চাইলে আমার ব্লগ ঘুরে আসতে পারেন। এক দশক আগে পরের নেত্রকোনা ভ্রমণের একটি পিডিএফ-ও রয়েছে সেখানে, চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ধন্যবাদ।)
(৩য় পর্ব)
সর্বশেষ এডিট : ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ রাত ১২:১৯


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।