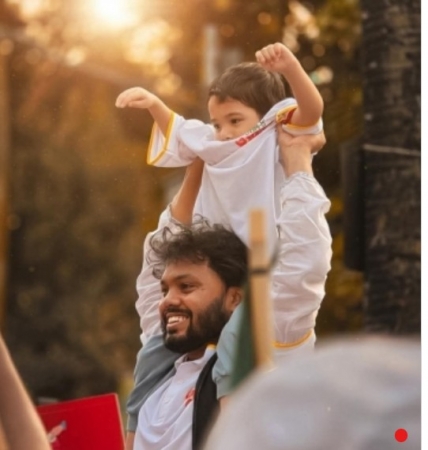গ্রামের নাম রসুলপুর। গ্রামের ঠিক মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে চলে গেছে সড়ক ও জনপথের চওড়া পিচের রাস্তা। রাস্তার দক্ষিণ পাশে একটু পরপর আয়তাকার বড় গর্ত। এই রাস্তাটি আগে মাটির ছিল। তারপর যখন সরকারের কাবিখার (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) আওতায় রাস্তা বড় করা হয় তখন ঐ গর্তগুলি কেটে মাটি তোলা হয়েছিল রাস্তায়। এরপর আরো উন্নত হয়ে মাটির রাস্তা হল পিচঢালা রাজপথ। রাস্তাটাকে ৯০০ কোণে ছেদ করে বয়ে গেছে একটি খাল। এই খালের নাম কি তা কেউ জানে না। খালের উপর একটি সিমেন্টের কালভার্ট। কালভার্টের নিচ দিয়ে খালটি সোজা এগিয়ে গেছে প্রায় ১ কিলোমিটার। তারপর ডান দিকে টার্ন নিয়েছে। এই টার্নিং পয়েন্টেই গ্রামের কবরস্থান। রাস্তার উত্তর পাশেই এবং খালের পূর্ব পাশেই কালভার্টের গোড়াতে ওলিদের বাড়ি। রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকতেই রাস্তার সমান্তরালে তিনটি টিনের ঘর। একটি গোয়ালঘর, একটি গুদাম ঘর অপরটি কাছারিঘর। এই তিনটি ঘরের মাঝে মাঝে কাগজিফুল-জবাফুল-বকুল ফুল-কৃষ্ণচুড়া এবং বেলের গাছ। আরেকটু উত্তরে এগিয়ে গেলে বড় উঠান, গরুর গোবর দিয়ে সুন্দর করে লেপে রাখা হয়েছে উঠানটি। উঠানের উত্তরে দক্ষিণমুখী টিনের বড়ঘর। এখানেই থাকে ওলিরা। বড়ঘরের সাথে পশ্চিম দিক লাগোয়া রান্নাঘর। রান্নাঘরের পশ্চিমেই খালের পাড়।
বড় ঘরের পিছনে অর্থাৎ উত্তর দিকে ঘন জঙ্গল। সেখানে আছে নারিকেল-সুপারী, আম-জাম, কাঁঠাল-লিচুর ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের উত্তরে উলু বন। সেখান থেকে বছরে একবার ছন কেটে আনা হয়। আবার একা একাই ছন জন্মায়। উলু বনে আছে প্রচুর খেজুর গাছও। প্রতি শীতে এই খেজুর গাছ থেকে আসে শত শত ঠিলা খেজুর রস। শীতের সকালে ঠিলা থেকে রস কাচের গ্লাসে ঢাললে তা বিয়ারের মত দেখায়। ঐ রকম রঙ, ঐ রকম একটু ফেনাও ওঠে। খেলে একটু নেশা নেশা ভাবও আসে। তবে বেশি নেশা তালের রসে। ৮% কনসেনট্রেশনের বাভারিয়া বিয়ার এই তালের রসের কাছে কিছুই না। নেশার বস্তু আরও আছে, ‘পাগলা সুপারিÑবিষপান” এক টুকরা মুখে নিয়ে চাবালেই গা গরম হয়ে যায়, মাথা ঘোরে। দুই চার জনের বাড়িতে গাঁজার গাছও আছে। এই উলুবন পর্যন্ত ওলিদের জায়গা তারপর কবরস্থান। কবরস্থানের দুই পাশে খাল।
আগে এই গ্রামের নাম ছিল দুর্গাপুর। গ্রামের ৯০% পরিবার ছিল হিন্দু। ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১ এ ধীরে ধীরে হিন্দুরা দেশ ছেড়েছে। আর একে একে হিন্দুদের বাড়ি-জমি দখল করেছে মুসলমানেরা। অধিকাংশই জোর করে দখল করা, তবে কেউ কেউ নামমাত্র মূল্যে কিনেও নিয়েছে হিন্দুদের কাছ থেকে। এরপর শুরু হয়েছে পরিবর্তন। প্রথমেই নির্মিত হল একটি মসজিদ। ভারতের দেওবন্দ থেকে পাশ করা এক মৌলানা এলেন ইমাম হয়ে। মসজিদ সংলগ্ন জায়গায় নির্মিত হল মাদরাসা। একদিন জুমার নামাজের আগে ইমাম সাহেব ঘোষণা করলেনÑ
“এতবড় একটা গ্রাম, এত মুসলমান বাস করে, কারো বুকে কি এতটুকু পাটা নেই গ্রামের নাম পরিবর্তন করতে? এত মুসলমান থাকতে গ্রামের নাম দূর্গাপুর হয় কিভাবে? গ্রামের নাম হবে রসুলপুর।”
পপ-প-পয়য়য়য়...দ্রিম-দ্রিম-দ্রিম... রসুল বনাম দূর্গা। লড়াই। লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। পাটা আছে বৈকি। তার উপর ইমাম সাহেব তার শক্ত-লম্বা-গোল পুতা দিয়ে যে ঘষা দিলেন তাতে সবগুলি বুকের পাটাই কেঁপে উঠল। ঐ দিন বিকালেই মসজিদের সামনে সাইনবোর্ড লাগানো হল “রসুলপুর দারুল ইহসান মসজিদ ও মাদরাসা”। তিনটি মন্দির ছিল গ্রামে। সেখানে যে দেব-দেবীরা বাস করত তারাও বুঝল সেই দিন আর নাই, দিন বদলায়ে গেছে। তাই তারাও রাতের আঁধারে একে একে কেটে পড়ল সুযোগ বুঝে। ইদানিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা শান্তিপূর্ণ কালচার চালু হয়েছে। ইলেকশানের দিন রাতে যে দল হেরে যায়, সেই দলের ছাত্র সংগঠন ঐ রাতেই হল ছেড়ে পালিয়ে যায়। বিজয়ী দলের ছাত্র সংগঠন বিনা বাধায় হলগুলি দখল করে নেয়। পাঠক নিশ্চই বুঝতে পারছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যা ২০০১ বা ২০০৮ সালে করেছে হিন্দু দেবদেবীরা তাই করেছিল ১৯৪৭ এ ১৯৭১ এ। এতটুকু অ্যাডভান্স না হলে কি আর দেবদেবী হওয়া যায়? দূরদর্শী দেবী!
যাই হোক দেবদেবীরা কিভাবে কখন কোথায় চলে গেল তা জানা না গেলেও তিন বছরের মাথায় দেখা গেল মন্দির তিনটির একটি স্থানীয় মেম্বার “বীরমুক্তিযোদ্ধা”র বৈঠকখানা, অন্য একটি “সবুজ সংঘ যুব ক্লাব” এর অফিস এবং শেষটি ইমাম সাহেবের কোয়ার্টার। এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। গ্রামে এখন হিন্দু নেই বললেই চলে। কিন্তু এখনও গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই কৃষ্ণচূড়া-রক্তজবা-কাগজিফুল-গাদা-বেলী-বেল গাছের বাহার। মুসলমান বাড়িতে সাধারণত এত ফুল গাছ থাকে না। কিন্তু এই গ্রাম ভরা ফুল গাছ। মহানবী নাকি ফুল খুব পছন্দ করতেন। তিনি নাকি বলেছেন, “একটি পয়সা পেলে খাবার কিনো আর দুটি পয়সা পেলে ফুল কিনো”। যাক তাতেই রক্ষা! হিন্দু দেবদেবীর পূজার ফুল ধর্মান্তরিত হয়ে জীবন রক্ষা করল। জান বাঁচানো ফরজ!
কপাল পুড়ে ছিল শুধু তুলসি গাছের। বেচারা তুলসি গাছের নামের সাথে হিন্দুধর্মের ব্রান্ড খুব ভালোভাবে লেগে আছে। তাই কোন এক সবেবারাতের রাতে মাদরাসার সব ছাত্ররা মিলে গ্রামের সব তুলসি গাছ উপড়ে ফেলে দিয়েছিল। শুধু অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হিসেবে বীরমুক্তিযোদ্ধা মেম্বার সাহেবের বৈঠকখানার সামনের তুলসি গাছটা এখনও জীবন্ত। অসাম্প্রদায়িকতা চিরজীবী হোক!
শত শত বছর ধরে এই গ্রামে একটি মেলা বসত। সেটি এখনও বসে, তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওয়াজ মাহফিল। দোয়া খায়ের।
এখন যেখানে কবরস্থান আগে সেখানে শ্মশান ঘাট ছিল। কালের সাক্ষী হয়ে এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে জংধরা একটা লোহার পিলার। বাকি তিনটা পিলারের কপালও নিশ্চই দেবদেবীদের মতোই। তবে তারা বেশি দূর পালাতে পারেনি। দা-কাচি-বটি হয়ে এই গ্রামেরই কোন না কোন রান্নাঘরে আছে। আপনারা তো জানেন হিন্দুধর্মে জন্মান্তরবাদের ধারণা প্রচলিত। শ্মশান ঘাটের লোহার পিলার জন্মান্তরে দা-কাচি-বটি হয়ে মুসলমানের রান্নাঘরে বেগুন কাটে। গরুর গোস্ত কাটে। জয় জন্মান্তরবাদ!
এই গ্রামের আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল, সবাই কি যেন খুঁজছে। বড় বটগাছের গোড়ায়Ñপুরান মন্দিরের আশেপাশে কেউ পুকুর কাটলে বা কোন কারণে মাটি খুড়লে সবাই তাকিয়ে থাকে। প্রতীক্ষায় থাকে কোন কিছুর। হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় যেটুকু পেরেছে সাথে করে নিয়ে গেছে। আর যা পারেনি তা মাটিতে পুতে রেখে গেছে। তাদের চিন্তা ছিল, যদি কোন দিন ফিরে আসতে পারে সেদিন তুলবে আর যদি ফিরে আসতে না পারে তাহলে ভগবান বসুন্ধরার কাছে জমা রইল (বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা নয়)। গ্রামের অনেকেই পেয়েছে সোনার টাকা, রুপার টাকা ভর্তি পিতলের বদনা-ঘটি-কলসি। জন্মান্তরে তারাও হয় মুসলমানের অন্দরে কানেরতাÑনাকেরতাÑহাতেরতা হয়েছে বা জুয়ার আসরে মুসলমান জোয়ানের বাহু আরও শক্ত করেছে। কার্ড পেটানোর শব্দ আরও লাউড করেছে। এ কারণেই গ্রামে সবাই নিম্নমুখী। সবাই খুঁজছে। কখন কি পাওয়া যায়। গ্রামের মানুষ এই টাকার নাম দিয়েছে “হনুমানের পয়সা”। অলৌকিক ক্ষমতা আছে এই হনুমানের পয়সার। আরও একটা জিনিস খোঁজে গ্রামের মানুষ, ম্যাগনেট। ব্রিটিশ আমলে জমির মাপ ঠিক রাখার জন্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে পিলার পোতা হতো। এই পিলারের মধ্যে থাকত শক্তিশালী “প্রাকৃতিক চুম্বক”। এই চুম্বকের এখন অনেক দাম, নাম ম্যাগনেট। ভূমি জরিপের কম্পাসের কাটা আকর্ষণের জন্যেই বসানো হতো এই ম্যাগনেট। এই ম্যাগনেটও সবাই খুঁজছে। সবাই চায় কোটিপতি হতে। কেউ গরিব থাকতে চায় না। দারিদ্রের জন্যে সবাই কপালকে দোষ দেয় আর অলৌকিক কিছু পাবার প্রতিক্ষায় থাকে কিন্তু পরিশ্রম করতে চায় না। সবাই চোখের পলকে বড়লোক হতে চায়।
এই গ্রামেরই এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত চাষী মোহাম্মদ আলী। তার দুই ছেলে হোসেন এবং ওলি। গ্রামে যখন কোন শিশুর জন্ম হয়, তার পরপরই মুরব্বিরা একটা কমেন্ট করে ঐ শিশু সম্পর্কে। যেমন, এই ছেলের চুল খাড়া, ও বড় হয়ে রাগী হবে। ওর নাক বোচা, ওর ভাগ্য ভালো হবে। তার দুই চোখের ভ্রু একসাথে মিলানো, সে বউয়ের ভালোবাসা পাবে। ঐ মেয়ে দেখতে তার বাপের মতো হয়েছে, ওর সংসার সুখী হবে। শেষ সন্তান মায়ের মতো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রামের শিশুরা চারপাশের এইসব কথা শুনতে শুনতে বড় হয়। শুনতে শুনতে এক সময় বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করতে করতে এক সময় মনের মধ্যে গেঁথে যায়। পরে দেখা যায় সে আসলেই ওই রকমই হয়েছে। যেমন ধরুন যার চুল খাড়া সে রাগীই হল, যে মেয়ের চেহারা বাবার মতো সে সুখী সংসারেই গেল। যার দুই ভ্রু জোড়া লাগানো সে তার বউয়ের অ-নে-ক ভালোবাসা পেল ইত্যাদি।
এর পিছনে অবশ্য দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, হাজার বছর ধরে গ্রামে গঞ্জে প্রচলিত মানুষের অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দ্বিতীয়ত, ছোটবেলা থেকে মানুষ যা শোনে, যা বিশ্বাস করে যা মনের মধ্যে গেঁথে যায় তা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না। ছোটবেলা থেকে সে তার যে গুনের কথা শুনতে শুনতে বড় হয়, নিজের অজান্তেই সে সেই রকমই হয়ে যায়।
দোষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমার মতে দ্বিতীয় যুক্তিটি প্রবল। মোহাম্মদ আলীর ২য় পুত্র ওলির যখন জন্ম হয় তখন তার দুই চোখ পুরোপুরি গঠিত হয়নি অর্থাৎ ফোটে নি। জন্মের সাত দিন পর সে প্রথম চোখ মেলে তাকিয়েছিল। তখন থেকেই গ্রামবাসীর এক আওয়াজ, এই ছেলে স্বাভাবিক নয়, অন্য রকম। ছোটবেলা থেকে ওলি শুনেছে সে অন্য রকম। কাজেই এর একটা প্রভাব তো তার জীবনে পড়বেই। ছোটবেলা থেকেই সে অন্য রকম। বাচ্চারা সাধারণত খুব কাঁদে। ওলি তেমন কাঁদত না। তিন বছর বয়সেও সে ভালো করে কথা বলতে শেখে নি। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত।
এই ওলিই হল এই উপন্যাসের নায়ক। যেন তেন নায়ক নয়, স্বয়ং বাংলা সিনেমার নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন। সে রাজার ছেলে, ভালোবাসে বেদের মেয়ে জোছনাকে।
বেদের মেয়ে জোসনা আমায় কথা দিয়েছে-
আসি আসি বলে জোছনা ফাঁকি দিয়েছে।
মারজুক রাসেল আবার অন্য এক জোছনার কথা লিখেছেÑ
চাঁদের মেয়ে জোছনা আমি বেদের মেয়ে না,
কথা দিলে কথা রাখি ফাঁকি দেই না।
ইলিয়াস কাঞ্চনের জোছনা তাকে ফাঁকি দিয়েছিল কিন্তু মারজুক রাসেলের জোছনা তাকে ফাঁকি দেয়নি। কিন্তু আমি তো জানি যুগে যুগে জোছনাদের চরিত্র একই। তারা একই ভাবে পুরু ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে হাসে, একই ভাবে মায়া কান্না কাঁদে। একই জিনিস চায়, একই জিনিস হারায়। তাহলে ইলিয়াস কাঞ্চনÑ মারজুক রাসেল?
জোছনারা মানুষ নয়, দেবী হতে চায়
ফুল চায়, প্রনাম চায়,
পুজো শেষে লোকে তাই ছুঁড়ে ফেলে দেয়।
ইলিয়াস কাঞ্চন এখনও পূজা করেননি। সিঁদুর-ধুতি পরে পূজা করার ধান্দায় আছেন। এ কারণেই তার দেবী-জোছনা তাকে ফাঁকি দিয়েছে। মারজুক রাসেলের পূজা শেষ। সে প্রসাদ খেয়ে ফেলেছে চেটেপুটে। পূজার প্রসাদ পবিত্র, অনেক সওয়াব। পূজার আগে দেবীরা ফাঁকি দেয়, পূজারী-ব্রাহ্মণ তাদের পিছ পিছ ঘোরে। যেমন ইলিয়াস কাঞ্চন। পূজা শেষে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ফাঁকি দেয়, দেব-দেবীরা তাদের পিছ পিছ ঘোরে। যেমন মারজুক রাসেল। দেবী আর পুরোহিতের পলাপলি খেলা। এক-দুই-তিন---তিলো!
ছোটবেলায় যখন বাংলা সিনেমার নায়ক-নায়িকার অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখতাম তখন শুনতাম, বাস্তবে নায়ক নায়িকা আসলে এত কাছে আসে না। এ সবই ক্যামেরার কারসাজি। এখন জানি, ক্যামেরায় যতটুকু দেখায় নায়ক-নায়িকা তার চেয়েও বেশি কাছে আসে। আর প্রয়োজক-পরিচালক নামের যে চরিত্রগুলিকে ছোটবেলায় চিনতামই না, এখন জানি তারা নায়িকার আরও বেশি কাছে আসে। একেবারে শরীরের ভিতরে ঢুকে যায়। কিন্তু এক শরীরে বেশি দিন ঢুকতে ভালো লাগে না প্রয়োজকÑপরিচালকদের। তারা নতুন শরীর খোঁজে। তখন শুরু হয় নতুন নতুন সুন্দরী প্রতিযোগিতা, বেহেসত থেকে নেমে আসে হুর পরীর দল। আমার কাছে “মিস বাংলাদেশ”দের মানুষ মনে হয় না। তারা মানুষ আর হুর পরীর সংকর প্রজননে তৈরি নতুন কোন প্রজাতি। যেমন ঘোড়া আর গাধার ক্রস প্রজননে খচ্চর হয়। খচ্চরের কাজ মালটানা আর মিস বাংলাদেশদের কাজ শরীর টানা। সবাই আছে টানাটানির উপর। টান টান উত্তেজনা! মারো টান হেইয়ো! আরো জোরে হেইয়ো!!
ওলি কার মত নায়ক, মারজুক রাসেল না ইলিয়াস কাঞ্চন? আচ্ছা কাহিনী আগে শেষ হোক, পরে এই হিসেব করা যাবে।


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।