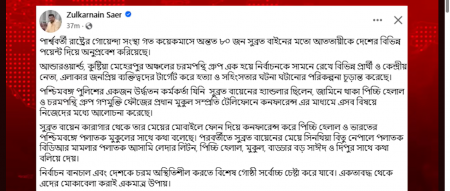২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে যে আগ্রাসন চালায় তার নেপথ্য কারণ শুধু ইরাক নামের তেলসমৃদ্ধ দেশটিকে দখল করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়াই নয়, তার সাথে সাথে ঠান্ডাযুদ্ধের পরবর্তী পুরো পৃথিবীর রাজনীতিতে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্যের জানান দেয়া। জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, একক সিদ্ধান্তে ইরাক দখল ও সাদ্দাম সরকারকে উচ্ছেদ করা, মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অনেক দেশের জন্যই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এক ধরণের সংকেত। এ যেন অন্যদের দেখিয়ে দেওয়া এ যুগে স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিতে হলে কি কি শর্ত – অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র নির্ধারিত- মেনে নিতে হবে। কিন্তু আগ্রাসন শুরু করার সময় বুশ প্রশাসনের অনেকেই হয়তো ভাবেননি বিশ্বজুড়ে নিজেদের একক আধিপত্য বা হেজেমনি টিকিয়ে রাখতে শুরু করা এ যুদ্ধ কোথায় গিয়ে ঠেকবে। তাই নিজস্ব শক্তির প্রদর্শন করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়, শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস করে জনগণকে নিরাপত্তাহীন ও দেশটিকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে। কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে ইরাকের ব্যর্থতার দায়ভার কখনই ইরাকের বর্তমান পুতুল সরকার বা জনগণের নয়, পুরোপুরি দেশটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনকারী যুক্তরাষ্ট্রের। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বজুড়ে একক পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে যে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ‘সফট পাওয়ার’ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহন করেছিল তা বুশ শাসনামলে প্রত্যাখ্যান করা হয়, নেয়া হয় শক্তিপ্রদর্শনের নীতি। এ নীতির বলি হওয়া ইরাকের জনগণকে যেমন অনেক প্রিয়জনকে হারাতে হয়েছে, বাস্তুচ্যুত ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করতে হচ্ছে, তেমনি ইরাকি জনগণের তুমুল প্রতিরোধের মুখে ইরাককে মধ্যপ্রাচ্যে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে নিজস্ব আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রদর্শনের যে উচ্চাকাঙ্খা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল তার অপমৃত্যু ঘটেছে।সাফল্যতো দূরের কথা এই আগ্রাসনকে এখন দেখা হচ্ছে যুক্তরাষ্টের অন্যতম ভুল হিসেবে। জানুয়ারি, ২০০৭ এ ২৫ টি দেশের ২৬ হাজার মানুষের মধ্যে বিবিসি পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় বিশ্বের ৭৩ ভাগ জনগণ এ যুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ এ তৎকালীন জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান ইরাক আক্রমনকে অবৈধ ও জাতিসংঘ চার্টারের লঙ্ঘন বলে অবহিত করেন। তাই বারাক ওবামার সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৮ মাসের মধ্যে সেনা অপসারণের ঘোষণা দিতে বাধ্য হন। ওবামার নির্বাচনী প্রচারণায়ও ইরাক যুদ্ধ একটি বড় ইস্যু ছিল। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ি সম্মান বজায় রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেনাদের কিভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা যায় তাই এখন ওবামা প্রশাসনের বড় মাথাব্যথা।
ইরাক আগ্রাসনের পেছনে বুশ প্রশাসন আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে বেশ কয়েকটি যুক্তি তুলে ধরে।গণবিধ্বংসী অস্ত্রের উৎপাদন, আলকায়েদাকে সহযোগিতা, ফিলিস্তিনি আত্মঘাতি বোমা হামলাকারীদের সহায়তা প্রদান ও সাদ্দাম সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন ছিলো এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বুশ সরকার শক্তি প্রদর্শনের যে নীতি গ্রহন করে তাতে আক্রান্ত হবার আগেই সম্ভবনাময় শত্রুর উপর হামলা চালানোকে বৈধতা দেয়া হয়।আর বুশ প্রশাসনের এমন পররাস্ট্রনীতির জন্য যেন টুইন টাওয়ারের মত একটি হামলাই বেশ দরকারী ছিল। তাই টুইন টাওয়ারে হামলা বুশের শক্তি প্রদর্শনের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বব্যপী জাহির করতে টনিকের মতই কাজে দেয়। ফলে রিচার্ড চেনি বা ডোনাল্ড রামসফেল্ডের মত বুশের সহচররা খুব সহজেই আলকায়েদা দমন ও আলকায়েদাকে সাহায্য করতে পারে এমন দেশ বা গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে বা তৈরির চেষ্টা করছে এমন দেশগুলোর বিরূদ্ধে যুদ্ধের এক মহাপরিকল্পনা হাতে নেয়। ২৯ জানুয়ারি ২০০২ এ প্রেসিডেন্ট বুশ তার স্টেট অব ইউনিয়ন বক্তৃতায় ইরাক, ইরান, উত্তর কোরিয়া ও তাদের সন্ত্রাসী মিত্রদের এক্সিস অব ইভিল বা শয়তানের অক্ষশক্তি হিসেবে অবহিত করেন। এভাবেই বুশ প্রশাসন ইরাক আগ্রাসনের মত একটি অযৌক্তিক সিদ্ধান্তর যৌক্তিকতা প্রমাণ করে তা আমেরিকার জনগণের কাছেও যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে গ্রহনযোগ্য করে তুলে।
বুশ প্রশাসনের কাছে সাদ্দাম সরকার বিশ্বব্যপী যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রাধ্যান্য বা হেজেমনি স্থাপনের পথে একটা বড় ক্ষত হিসেবে দেখা দিয়েছিল। নব্বুই দশকের শুরুতে উপসাগরীয় যুদ্ধ, বারবার আরোপ করা অর্থনৈতিক অবরোধ অথবা বিমান হামলা কিছুই যেন মার্কিন আধিপত্যের সামনে বাথ পার্টির মাথা নোয়াতে পারছিলনা। মার্কিন হেজেমনি প্রমাণের পাশাপাশি এ যুদ্ধের আরো একটি বড় কারণ হিসেবে দেখা হয় প্রভাবশালি মিলিটারি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সগুলোর চাপকেও। অস্ত্র তৈরি, সামরিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, যুদ্ধ পরবর্তী পুননির্মান ইত্যাদি লাভজনক খাতের চাপে এ সময় যেকোন একটি যুদ্ধের দরকার ছিলো বলে অনেকে মনে করেন।( Stephen C. Pelletie`re‘Losing Iraq, Insurgency And Politics’)বারবার অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে দেশটিকে দুর্বল প্রতিপক্ষ হিসেবেও ভেবেছিল বুশ প্রশাসন। এছাড়া,সাদ্দামের একনায়কতন্ত্র, গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির অভিযোগ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস এসব অস্ত্রব্যবসায়ীদের কাছে ইরাককে যুদ্ধবাজারের নতুন পণ্য করে তুলে।
গণবিধ্বংসী অস্ত্র উৎপাদনের যে অভিযোগ এনে ইরাকের উপর হামলা চালানো হয়েছিল তার অসারতা প্রমান হয়েছে। ২০০৩ এর মার্চে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণ, যাচাই ও তদন্ত কমিটির শীর্ষ তদন্ত কর্মকর্তা হান্স ব্লিক্স জানান, ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি বা এ ধরণের কার্যক্রমের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইরাক দখলের পরও যুক্তরাষ্ট্র
এ সংক্রান্ত কোন প্রমান দেখাতে ব্যর্থ হয়। ইরাক আক্রমনের আরেকটি কারণ হিসেবে সাদ্দাম সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে যুক্তিটি দেখানো হয় তা আবু গারাইব কারাগারে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের চালানো অকথ্য নির্যাতনের কাছে বেশ ম্রিয়মান হয়ে উঠে। বন্দী নির্যাতনের ঘটনা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র আসলেই কতটুকু যোগ্য তার উপযুক্ত প্রমানও দেয়।
ইরাক আগ্রাসনের আগে বুশ প্রশাসন হয়ত ভেবেছিলো সাদ্দাম শাসনামলে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল, সেই ব্যবস্থাকেই ব্যবহার করে অল্প সংখ্যক সেনা মোতায়েনের মাধ্যমে ইরাক দখল ও নিজেদের মনমত একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কন্ডোলিজ্জা রাইসের ভাষায় ‘The concept was that we would defeat the army, but the institutions would hold, everything from ministries to police forces.’
(Michael Gordon, ‘Catastrophic success”: The strategy to secure Iraq did not foresee a 2nd war’, New York Times, 19 October 2004.)
রাইসের এ মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি। ইরাকের সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাই আগ্রাসনের ফলে ভেঙে পড়ে, মার্কিন সেনাদের অবস্থান এর সময়সীমা বাড়তে বাড়তে আট বছরে ( ২০০৩- ২০১১)গিয়ে ঠেকেছে। ইরাকের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পেছনে অনেকেই দায়ী করেন বুশ প্রশাসনের নেওয়া ভুল সিদ্ধান্তকে। প্রথমত ইরাকে নিযুক্ত প্রোকনসাল পল ব্রেমার এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ি ইরাক জুড়ে শুরু হয় ডিবাথিফিকেশান বা বাথ পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে গ্রেফতার বা চাকরি থেকে অপসারণের প্রক্রিয়া। ব্রেমারের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ি ইরাকি সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেয়া হয়, এর ফলে ৪ লক্ষরও বেশি দক্ষ ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইরাকি সেনা তাদের চাকরি হারান(Toby Dodge,‘Grand ambitions and far-reaching failures,The United States in Iraq’)। এই দুই সিদ্ধান্তের ফলে ইরাকজুড়ে বড় ধরণের নৈরাজ্য ও ক্ষোভ তৈরি হয়। তাই সাদ্দামের পতনের প্রথম দিন থেকেই যে লুটপাট ও সহিংসতা শুরু হয়, তা মার্কিন সেনারা কোনভাবেই থামাতে পারেনি। বিশেষ করে দক্ষিন ও মধ্য ইরাকে এক ধরণের নিরাপত্তা শূন্যতার তৈরি হয়। আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনা তো আছেই, সেই সাথে চাকরি হারানো সেনা সদস্যদের ক্ষোভ, দেশজুড়ে বাথ পার্টির লুকানো অস্ত্র ও মার্কিন সেনাদের প্রতি ঘৃণা বড় ধরণের প্রতিরোধ গড়ে তুলে। প্রাথমিক প্রতিরোধ ধর্মীয় ও জাতিগত চেতনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সংগঠিত করে হয়ে উঠে।
২০০৫ সালে মার্কিন বিরোধী ৫টি দল গড়ে উঠে। ইসলামিক আর্মি ইন ইরাক, সুন্নাহ আর্মি, মুজাহিদিন আর্মি, মুহম্মদ’স আর্মি এবং দি ইসলামিক রেজিসট্যান্স মুভমেন্ট ইন ইরাক নামের এ দল পাঁচটি মার্কিন সেনাদের উপর চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে যেতে থাকে (International Crisis Group, ‘In their Own Words: Reading the Iraqi Insurgency’, Middle East Report, no. 50, 15 February 2006)
মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সাথে সাথে নিজেদের মধ্যে জাতিগত হানাহানি বাড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হয় ‘সালাফিজম’ এর প্রভাবকে। এ মতবাদে দখলদার সেনাদের পাশাপাশি তাদের সহযোগি বা যারা ধর্মের সঠিক পথে অনুসরণ করছেনা এমন মুসলমানদেরও হত্যা করা জায়েজ হিসেবে দেখা হয়। ইরাকে সালাফিজম মতবাদ অবলম্বনকারী অনেক যোদ্ধাই (শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ)অন্য দেশ থেকে আসা, এদের উপর আলকায়েদার নিয়ন্ত্রন রয়েছে বলে মনে করা হয়। এছাড়া ৬০ হাজার থেকে ১ লাখ মিলিশিয়া বাহিনীও মার্কিন ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়( Larry Diamond, ‘Squandered Victory: The American Occupation and the Bungled Effort to Bring Democracy to Iraq’)এদের মধ্যে ইরানের সমর্থনপুষ্ট ও ইরানিয়ান রেভুলেশনারি গার্ড এর ট্রেনিংপ্রাপ্ত বদর ব্রিগেড ও মুকতাদা আল সাদরের মাহদি আর্মি উল্লেখযোগ্য।
জাতিগত সংঘাত, মার্কিন সেনা ও তার মিত্রবাহিনীর হামলায় ইরাকে মানবেতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ২০০৮ সালের এক জরিপে দেখা যায় দেশটিতে গৃহহীন ৪৭ লক্ষ মানুষ যা ইরাকের মোট জনসংখ্যার ১৬ ভাগ। ২০০৭ সালে চালানো আরেকটি জানা যায় ইরাকি শিশুদের শতকরা ৩৫ ভাগই এতিম। সাদ্দাম শাসনামলে অর্থনৈতিক অবরোধ ও বাথ পার্টির স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ইরাকি জনগণ খুব বেশি স্বস্তিতে না থাকলেও সেটি ছিলো তাদের নিজেদের সরকার।তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সাদ্দাম শাসনামলের চেয়ে অনেক দিক থেকেই বৈরি পরিস্থিতির মুখোমুখি ইরাকের জনগণ। এ পরিস্থিতি তাদের জন্য এতই অসহনীয় যে, জানুয়ারি ২০০৬ সালের ইউএস কমিশন্ড ওপিনিয়ন পোল অনুযায়ি দেখা যায়, শতকরা ৮২ থেকে ৮৭ ভাগ ইরাকি মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধী, আর শতকরা ৪৭ ভাগ ইরাকি মার্কিন সেনাদের উপর হামলা চালানোকে সমর্থন করে।
যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমনের পেছনে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার ও অর্থনৈতিক কারণ দুটিই ছিল। পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে পরিবর্তন করতে একটি মুক্তবাজার অর্থনীতির ও মার্কিন প্রেসক্রিপশনের গণতান্ত্রিক সরকার ইরাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষমাত্রা যুক্তরাষ্ট্রের। যুক্তরাষ্ট্রের এ প্রচেষ্টা যে তেমন সফল নয়, তা ইরাকের ভঙ্গুর অর্থনীতি ও জাতিগত বিভেদময় রাজনীতি দেখেই বোঝা যায়। যুক্তরাষ্ট্র ইরাক জুড়ে যে শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেই ব্যর্থ হয়েছে তাই নয় সেই সাথে আরো বেশি সহিংসতা ও জাতিগত হানাহানির জন্ম দিয়েছে। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজুড়ে হেজেমনি প্রতিষ্ঠা করার উচ্চাকাঙ্খার এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, যার মাধ্যমে পুরনো কথাটি আবারো প্রমান হয়, জোর করে চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তন কথনই স্থায়ী হয়না। আর সংঘর্ষের নীতি ব্যবহার করে যেকোন দেশেই, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনাও বেশ কঠিন। বারাক ওবামার সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেনা অপসারণের নতুন সময়সীমা ঘোষণা করলেও তা কতটুকু বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আর যদি বাস্তবায়িত হয়ও, তারপরও ইরাক নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত শক্তিশালি যে নিকট ভবিষ্যতে হতে পারবেনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।
সাইমুম পারভেজ। প্রভাষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।