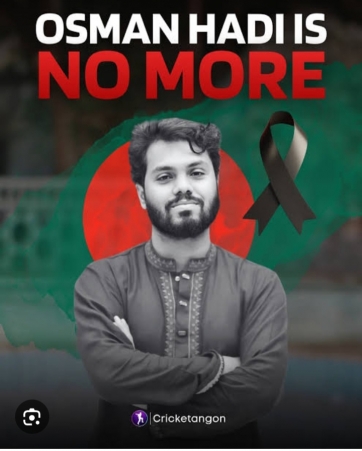বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন যেন ধনীদের বিলাসিতা, আর গরিবের জন্য এক প্রকার প্রহসন। সংবিধানে স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বাস্তব চিত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত। দেশের বহু মানুষ এখনও ন্যূনতম চিকিৎসা সেবা থেকেও বঞ্চিত। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জন্য এই ব্যবস্থাটি যেন মৃত্যু আর অসহায়ত্বের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এদেশে গরিবের বাঁচা মরা দুইই সমান।
এক সহকর্মীর স্ত্রীর অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি—সাধারণ পেটব্যথা নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। পরিবারটি ডাক্তারকে বিশ্বাস করে তার পরামর্শ অনুযায়ী একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। পাঁচদিন পর ছুটি মেলে, কোনো জটিল অস্ত্রোপচার হয়নি, হয়নি কোনো উচ্চপর্যায়ের চিকিৎসা—তবুও বিল গুনতে হয়েছে প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা! লাভ একটাই হয়েছে, অপ্রয়োজনীয় প্রায় ডজনখানেক ডায়াগনোস্টিক টেস্ট! এমন অভিজ্ঞতা শুধু তার নয়, দেশের হাজার হাজার পরিবারের।
সরকারি হাসপাতালের চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। সরকারি হাসপাতালগুলোতে গেলে চোখে পড়ে দীর্ঘ লাইন, সীমিত জনবল, অপ্রতুল যন্ত্রপাতি এবং অধিকাংশ সময় চিকিৎসকের অনুপস্থিতি। চিকিৎসা নিতে এসে অনেকেই দিনের পর দিন অপেক্ষায় থেকে শেষে হাল ছেড়ে দেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ দিনের বেশি সময় দেন বেসরকারি ক্লিনিক ও চেম্বারে, আর সরকারি দায়িত্ব পালন হয়ে পড়ে ‘কাগুজে দায়সারা’। হাসপাতালে ওষুধ নেই, ইমারজেন্সি সেবায় গাফিলতি—এসব যেন নিত্যদিনের চিত্র।
বেসরকারি হাসপাতালে চলছে সেবার নামে শোষণ। প্রাইভেট হাসপাতালগুলো যেন ব্যবসার অদৃশ্য চোরাবালি। সেখানে ডাক্তার নেই, মানুষ নেই—কিন্তু বিল আছে। প্রতিটি সেবার জন্য দিতে হয় আকাশছোঁয়া মূল্য। বেশিরভাগ সময় রোগীদের এমনসব পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়, যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নবিদ্ধ। ভুল রোগ নির্ণয়, অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার, ওষুধের দৌরাত্ম্য—এসবই মুনাফাকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার কুফল।
মানবিকতা নয়, এখন চিকিৎসাও একটি বাণিজ্য। একসময় চিকিৎসা ছিল সেবার ব্রত, এখন তা লাভের পণ্যে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসা একটি মৌলিক অধিকার হলেও বাস্তবে তা শুধুই আর্থিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিও আজ চিকিৎসা খরচের চাপে দিশেহারা। অনেকে চড়াসুদের ঋণ করে, ভিটেমাটি বিক্রি করে বাঁচার আশায় হাসপাতালে ছোটেন, কিন্তু চিকিৎসার নাম করে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হয়।
সমাধান কী? চিকিৎসা খাতে এই বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে—
সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো। যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার, নার্স এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেক নাগরিকের নির্দিষ্ট একটি লিমিট পর্যন্তু সরকারি খরচে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণে কঠোর মনিটরিং। বিলের স্বচ্ছতা, চিকিৎসার মান, রোগ নির্ণয় পদ্ধতির উপর নজরদারি বাড়ানো জরুরি। স্বাস্থ্য বীমা ও ভর্তুকি প্রণয়ন। গরিব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা গ্রহণ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাস্থ্য বীমা চালু করতে হবে। গ্রামীণ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যেন মানসম্মত চিকিৎসা পৌঁছে যায়, সেদিকে নজর দিতে হবে।
চিকিৎসা যেন কেবল ধনীদের জন্য সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার হয়ে ওঠে—এটাই হওয়া উচিত একটি কল্যাণরাষ্ট্রের লক্ষ্য। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলা সরকারি সেবাগুলোতে যখন তারা নিজেই বঞ্চিত হয়, তখন রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। স্বাস্থ্য খাতে এখনই যদি বৈষম্য কমাতে জরুরি পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এই বৈষম্য শুধু মানবিক নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটও তৈরি করবে।
"একটি রাষ্ট্র কতটা সভ্য, তা বোঝা যায় তার চিকিৎসা ব্যবস্থা দেখে। আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, সেটা ভাবার সময় এখনই।"
সর্বশেষ এডিট : ০১ লা জুলাই, ২০২৫ বিকাল ৩:৩৯


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।